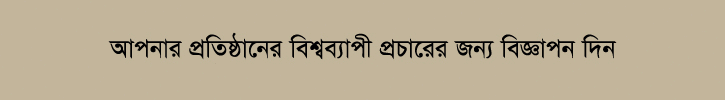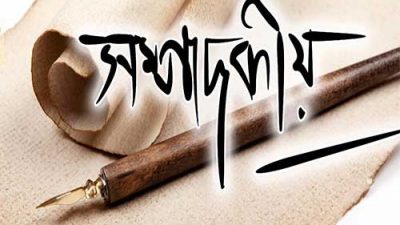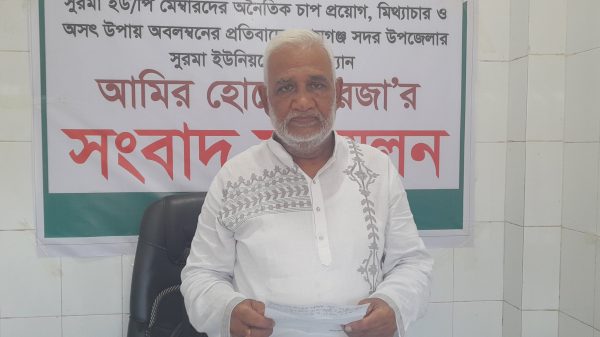বিশুদ্ধ অমূর্তচিন্তন জাগ্রত হোক : আশরাফ হোসেন লিটন
- আপডেট সময় রবিবার, ২১ মে, ২০১৭

সামাজিক দায়বদ্ধতা আর নিয়মতান্ত্রিক পন্থার মধ্য দিয়ে মন যা চায় তাই করি। সেই চাওয়াতেই একদিন ছুটে গিয়েছিলাম দর্শন শাস্ত্র পড়তে। অন্যান্য বিষয়ে সুযোগ পেয়েও মনের কাক্সিক্ষত পঠিতব্য দর্শন বিষয়ের বাস্তব প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করেও অন্তর উপলব্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম সেদিন। আজ অনেক দিন পর সে বিষয়ে কিছু লিখতে কলমের নিব লাগালাম সাদা কাগজের পাতায়।
আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি সুপারসনিক ফাইটার বিমানের নাম শুনেছি যা শব্দের গতির চেয়েও দ্রুত চলে। কিন্তু তার চেয়েও আরও অধিকতর গতিসম্পন্ন একটি বস্তু আছে যার নাম “মন”। মানুষের মনের চাইতে আর কোন কিছুই এত দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে পারেনা। মনের ভিতর ডুব দিয়ে একপলকে বিশ্ব ব্রহ্মা-কে ঘোরা যায়। এই নিভৃত মনের মাঝেই যখন অজানাকে জানার আগ্রহে অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খায়, সেই অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশ্নার্ত জিজ্ঞাসার উৎস থেকেই দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল ইতিহাসের এক ধূসর যুগে। যা আজকের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরম ক্রান্তিকালে এসেও দর্শন আমাদের কাছে তার স্বকীয় মহীমায় দীপ্ত এবং স্ববৈশিষ্ট্যে বহমান। রহস্যঘেরা এজগৎ সংসারের গুঢ় তথ্য রহস্য উদ্ভাবনের অন্তহীন প্রচেষ্টায় মানুষ সর্বদা তৎপর। ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলে দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ বর্তমানে আমাদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনচর্চার সাথে একান্ত হয়ে উঠেছে। দর্শনের ব্যাপকতার কারণে এক কথায় কেউ দর্শনের সংজ্ঞা দিতে পারেনি। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে দর্শনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,ÒWonder is the father of Philosophy”| । তবে একটু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান, গুঢ়রহস্য ও যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণই হচ্ছে দর্শন। এই নিরিখে তার তিনটি শ্রেণি বিন্যাস রয়েছে। একটি হচ্ছে- বাস্তবতার প্রকৃতি, অন্যটি হচ্ছে মানবিক বুদ্ধিমত্তার উৎস, তথা প্রকৃতি পদ্ধতি ও সীমারেখা এবং শেষটি হচ্ছে মূল্যবোধ। আর দর্শনের পরিভাষায় এদের নাম হচ্ছে পরাতত্ত্ব (Mola Physics), , জ্ঞানতত্ত্ব (Epis Physics) ) ও মূলতত্ত্ব(Axiology) দর্শন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। দর্শন যেহেতু ‘জীব-জগৎ-মন’ নিয়ে আলোচনা করে, সে কারণেই এটি মানব জীবনের সাথে অতপ্রোতভাবে জড়িত। এক অর্থে সব মানুষই দার্শনিক। কেননা মানুষের মধ্যে যখন বোধশক্তি জাগ্রত হয় তখন সে চিন্তা করে তার অস্তিত্বকে নিয়ে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তার আগমনের সত্যের প্রত্যক্ষ স্বরূপ উপলব্ধি করে বিধায় প্রতিটি মানুষ একজন দার্শনিক। যারা এ সত্যের রহস্য উন্মোচন করতে চায় তারা প্রকৃত দার্শনিক। একজন সাধারণ মানুষের সাথে দার্শনিকের পার্থক্য হচ্ছে- সাধারণ মানুষ জগৎ জীবন সমন্ধে তার যে চিন্তা-চেতনা সেটি তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তাদের ভাবনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তা বিচার-বিশ্লেষণ করে না। কিন্তু একজন দার্শনিক এসব ধারণা যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে জগৎ জীবন সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে।
দর্শনের অন্যতম কাজ হচ্ছে এ জগতের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে এমন এক সুসংবদ্ধ ধারণা দেওয়া, যে ধারণার সঙ্গে মানুষের নৈতিক সৌন্দর্য্যগত এবং ধর্মীয় সম্পর্কীয় চেতনায় সঙ্গতি থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে এই দর্শন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বিরাজমান। যার কোন সত্যগত ভিত্তি নেই। এমনও বলা হয়- দার্শনিক মানেই নাস্তিক। অথচ ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, আল গাজ্জালী যাঁরা মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে একেক জন উজ্জ্বল নক্ষত্র। এসব ভ্রান্ত ধারণা, ধর্মের অপব্যাখ্যা, কুসংস্কার দূরিভূত করে মানুষের ঘুমন্ত সত্ত্বাকে দর্শনের আলোয় জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে দর্শনের শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোয় আলোকিত করতে হবে তার চারপাশ। তাহলে সমাজ হবে শুদ্ধ, স্বস্তি আসবে আমাদের অস্থির সমাজে।
আমরা ধর্মীয় মূল্যবোধ, সমাজিক দায়বদ্ধতা, নৈতিক শিক্ষা এসব থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি বলেই আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এত অরাজকতা। আমাদের বিবেক বোধকে জাগাতে হবে। বিবেকের আদালতে প্রত্যেকের জবাবদিহির মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা তথা ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশাসনের মাধ্যমে যদি মানুষের মানবিক মূল্যবোধের স্বরূপ বিকশিত করা না যায়। তাহলে কঠোর আইন কিংবা বিশেষ কোন আইনের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। আমাদের বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানে বলেন, মানব সভ্যতার বিকাশে দর্শনের অবদান অপরিসীম। দার্শনিক জ্ঞান থাকলে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে আইন মানে ও আইন মান্যকারী হয়। দর্শন ও আইনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। একটি অপরটির সম্পূরক ও পরিপূরক, একটি বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না। কেননা আইনের ভিত্তি অনেকাংশে দর্শনের ভিত্তির উপর নির্ভশীল। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬খ্রি.)।
প্রতিটি মানুষ ও জীবের এই পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে খুব ছোট্ট একটা সময় নিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি প্রত্যেকের ক্ষণিকের এই বসবাস। আজ আছি তো কাল নেই।
আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞান গতিময়তা এনে দিলেও ব্যক্তির সংবেদনশীল মনোভাবকে যে ধ্বংস করে ফেলেছে তা কিন্তু নয়। মানুষ সময়ের বাস্তবতায় যান্ত্রিকতা নির্ভর হতে পারে। কিন্তু তার মৌলিক অনুভূতি কখনই ধ্বংস হতে পারে না। হঠাৎ কারও মৃত্যু সংবাদে যেমন মন আঁতকে উঠে, তেমনি কোন আনন্দ বার্তাতেও মন উৎফুল্লতায় উদ্বেলিত হয়। উপমহাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী প্রয়াত ভূপেন হাজেরিকার সেই বিখ্যাত গান- “মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য।” কিছু মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃত মানসিকতায় অর্থ উপার্জনের নেশায় আজ উন্মাদ। গাড়ি হবে বাড়ি হবে আমার রাজ্যে হবে আমি রাজা। রুগ্ণ প্রজার হাড্ডিসার কঙ্কাল আমার বিবেচ্য নয়। জীবনের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাই বলে মনুষ্যত্বহীনতায় নয়। এই অন্ধ প্রতিযোগিতা পরিহার করতে হবে। প্রত্যেকের অবস্থানে যদি আত্মসন্তুষ্টি থাকে, তাহলে এ সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আসবে স্থিতিশীলতা অন্যদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও আসবে প্রশান্তি। দার্শনিক Cared তার Philosophy of Religion হ গ্রন্থে বলেন, There is no province of human experience there is no things in the whole realm of reality which lies beyond the domain of philosophy or to which philosophical investigation অর্থাৎ ‘মানব অভিজ্ঞতার এমন কোন দিক নেই, সমগ্র বিশ্বসভ্যতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা দর্শনের আওতার বাইরে পড়ে বা দার্শনিক অনুসন্ধানে কার্য যার দিকে প্রসারিত হয় না।’
দার্শনিক শিক্ষার মূল লক্ষই হচ্ছে সৃষ্টি জীবের উপকার সাধন। এই জন্যই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি জীব হিসাবে তার দুটি দিক আছে, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সেই ব্যবহারিক বুদ্ধির সুপ্ত বিবেক আর বিশুদ্ধ বুদ্ধির মানুষের অমূর্তচিন্তনকে যদি জাগানো যায়, তাহলে বাহ্যিক আনুষাঙ্গিক আয়োজনে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়বে না। সে নিজ থেকেই হবে সুনিয়ন্ত্রিত। আর তাতে মানব জীবনে আসবে শান্তি। সমাজ হবে সুশৃঙ্খলিত। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই।
যে জাতি যত বেশি শৃঙ্খলিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কর্মকা-ের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি সেই রাষ্ট্রের মানবসম্পদ উন্নয়নে সুশিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কোন বিকল্প নেই। প্রত্যেককে উপলব্ধি করতে হবে আমার অর্জিত শিক্ষা শুধু আমার জন্য নয়, আমার চারপাশকে সে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। জীবন শুধু আত্মকেন্দ্রিকতা আর ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার জন্য নয়, জীবন জীবনের জন্য। মনে রাখতে হবে- ‘এই পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, জীবন একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়।’
দার্শনিক শেক্সপিয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তি- We must endure our coming hence as our going thither, Ripeness is all
[লেখক : উপজেলা ব্যবস্থাপক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি., মোবাইল ব্যাংকিং, সুনামগঞ্জ।]