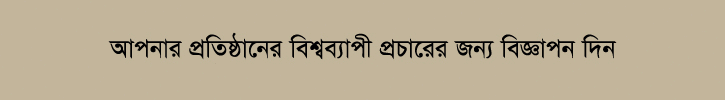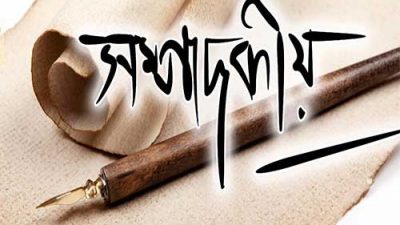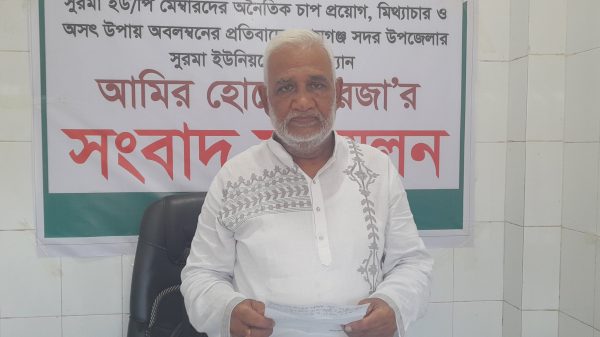ঝরাপাতার পান্ডুলিপি : শরর্ণাথী ৭১
- আপডেট সময় রবিবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

সুখেন্দু সেন ::
(পূর্ব প্রকাশের পর)
জেঠামশাইরা করিমগঞ্জে, এক কাকার পরিবার মেঘালয়ের সেলা বাজারে এবং আমরা শিলচরে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাঁই নিলেও বাবা তখন পর্যন্ত আমাদের আরেক কাকার পরিবারের সাথে বালাট ক্যাম্পে রয়ে গেছেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সেও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় শরণার্থী শিবিরের দুর্ভোগ হয়তো কিছুটা সহনীয় হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রজীবনে স্কাউট, যৌবনে ডন বৈঠকে গড়া শরীর। স্কাউট জাম্বুরিতে বার্মার জঙ্গলে পথ হারিয়ে এক রাত্রি গাছে চড়ে কাটিয়েছিলেন। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়ানোর অনেক গল্প শৈশবে বাবার কাছে শুনেছি। মাঝে মাঝে হার্নিয়ার ব্যথায় কষ্ট পেতেন। রান্নাবান্নার জ্বালানি সংকটে শিবিরের লোকজন যখন কাঠ সংগ্রহে পাহাড়ের টিলায় যেত তখন সকলের মানা সত্ত্বেও বাবা তাদের সঙ্গী হয়ে কচুর লতা, কলার মোচা, কাঁঠালের ইচড় সংগ্রহ করে আনতেন। বাঙালি-খাসিয়া বিরোধে বালাট শিবিরে কারফিউ চলাকালীন এক রাত্রিতে হার্নিয়ার ব্যথা প্রকট হয়ে উঠলে সবাই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল সেবার। কলকাতা থেকে আমাদের দাদা যখন বালাট গেলেন তখন তার সাথে চলে আসতে এবার আর অসম্মতি জানালেন না। দা-মনি বাবাকে শিলচর নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্য।
অস্ত্রোপচারে রোগ নিরাময় হল। শিলচরে অবস্থানকারী সবাই করিমগঞ্জের নিলাম বাজারের বাড়িতে চলে গেলেন। জেঠামশাই, জ্যেষ্ঠমাসহ সকলে আবার একত্রে বসবাস শুরু হল। কেবল এক দিদি এবং আমি দা-মনির সঙ্গে কলকাতার পথে পাড়ি দিলাম।
শিলচর থেকে ট্রেনে দুই রাত্রি দুই দিনের পথ কলকাতা। গৌহাটি পর্যন্ত প্রায় পুরোটাই পাহাড়ের উপর দিয়ে। নামটিও তাই- ‘পাহাড় লাইন’। বদরপুর থেকে লামডিং পর্যন্ত উপরে উঠার পালা। সেখানে থেকে ক্রমে সমতলমুখী। সড়কপথের মতো রেললাইন ইচ্ছে মতো আঁকা বাঁকা হতে পারে না। তাই অনেক পাহাড় এফোঁড় ওফোঁড় করে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ। পাহাড় যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে, সুড়ঙ্গ পথে সেটি অতিক্রম করে যায় রেলগাড়ি। ছোট-বড় ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি’র মতো সুড়ঙ্গ রয়েছে এ লাইনে। সামনে পিছনে রেল ইঞ্জিন। একটি টানছে অপরটি ঠেলছে। ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো উড়ে এসে চোখে-মুখে পড়ে। জামা কাপড়েও কালো দাগ লেগে যায়।
বেশ আগে জেঠামশাইয়ের কাছে আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানির কথা শুনেছিলাম। চট্টগ্রাম থেকে আখাউড়া-কুলাউড়া-বদরপুর হয়ে লামডিং পর্যন্ত অনেক জায়গায় শাখা-প্রশাখা খুলে দিয়েছিল এবিআর কোম্পানি। কেবল পাঁচ টাকার টিকেট কিনে সর্বত্র ভ্রমণ করা যেত। যাত্রীদের অধিকাংশই নাকি থাকতো চট্টগ্রাম, নোয়াখালির। এখন আর কোম্পানির যুগ নেই। সরকারি সংস্থা, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে। এখনো মনে হল বেশিরভাগ যাত্রীই পূর্ববঙ্গের। টিকেট লাগলো না, তবে শরণার্থী হিসাবে নয়, দা-মনি ইস্টার্ন রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা। রেলভ্রমণে রেলের চাকরিয়ানদের অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। যদিও পূর্বাঞ্চলীয় রেলের সকল সুবিধা উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রযোজ্য নয়, তবুও আন্তঃঞ্চল অলিখিত সমঝোতায় ম্যানেজ হয়ে যায় অনেক কিছু। রিজার্ভেশন বার্থও মিললো।
পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাঁকানো লাইন ধরে, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় সংযুক্ত করা ব্রিজের উপর দিয়ে শূন্যে, ঘুটঘুটে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গাড়ি ছুটছে। নিচে গভীর খাদ, দূর থেকে দূরে সারি সারি পাহাড়। বিরল জনপদ, দু’চারটি ছোটখাটো শহর। এগুলির কোনটি গড়ে উঠেছিল রেল লাইন নির্মাণকালীন সময়ে। দূরে পাহাড়ের ঢালে হঠাৎ এক পাল হাতিও দেখা গেল। বন মাঝে বন্যহাতি, এরকম দৃশ্যে পুলকিত হবারই কথা। কিন্তু দৃশ্যমান সৌন্দর্যের আকর্ষণ ছাপিয়ে চলমান ট্রেনের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে মন ছুটে পিছন ফিরে। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, প্রতিবেশী স্বজনদের স্মৃতি এসে ভিড় করে। শরণার্থী শিবিরের খুপরি ঘরে কেমন গাদাগাদি করে বসবাস করছে সবাই। বালাট বাজারের টংঘরে রাত্রিযাপন, মহাদেব শীল টেইলারের ঘরে আড্ডা, কং এর চা স্টলে চা খেতে খেতে সময় কাটানো, উদারবন্দ নয়ারাম হাইস্কুলের শরণার্থী ক্যাম্প, বীণাপানি লাইব্রেরির নতুন পরিচয়ের সঙ্গীরা, এসবই সাম্প্রতিক বিপর্যস্ত সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতি। জীবন্ত সজীব, মনের আয়নায় ঘুরে ফিরে ছায়া ফেলে।
শিলচরের ঠিকানায় দু’টি চিঠি পেয়েছিলাম। বালাটের পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। আগের মতো আড্ডায় অলস সময় কাটানো আর নেই। অনেক প্রতীক্ষা আর হতাশা কাটিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সুনীল শুক্লা, হিরন্ময় কর, মোসাদ্দেক ভাই, সাধন দা, মতিউর ভাই, আবু সুফিয়ান, মালেক হুসেন পীরসহ কয়েকজন প্রথম ব্যাচেই চলে গেছে যুদ্ধের প্রশিক্ষণে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে। ফণী চন্দ, স্বপন রায়, বিজিত ভট্টাচার্য্য, অরুণ দে ওরা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগ দিয়েছে রেডক্রসে। আমার নতুন ঠিকানা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চিঠিপত্রে আর কোনো খবরা-খবর জানা যাবে না। চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে এই প্রথম অনুভব করলাম কত দূরে সরে যাচ্ছি আমি। সবার কাছ থেকে কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।
ট্রেন বদল করতে হলো দু’বার। এতক্ষণ মিটার গেজে চড়েছিলাম। গৌহাটি পেরিয়ে বঙ্গাইগাঁও হতে ব্রডগেজ রেলওয়ে। অনেক বড় কামরা, জায়গা অনেক। রেললাইনও অনেক চওড়া। এরই মাঝে দুই রাত্রি পেরিয়ে গেছে। সকালবেলা গাড়ি ফারাক্কায় পৌঁছলো। নবনির্মিত বাঁধের উপর দিয়ে রেললাইন চালু হয়নি। গঙ্গা পেরুতে হয় ফেরি লঞ্চে। জ্যৈষ্ঠ শেষের বিশাল গঙ্গা। নদীর বুকজুড়ে শতশত জেলে নৌকা জাল ফেলে ইলিশ ধরছে। ইলিশ বলতে বরফে ডুবানো বাক্সবন্দী নরম সরম মাছই বুঝি। লাফানো ইলিশ এই প্রথম দেখলাম। ফেরিতে চায়ের স্টল, ভাতের হোটেল সবই আছে। ইলিশ ভাজির গন্ধে ম ম হয়ে আছে, ভিড়ে ঠাসা ফেরি। খাবার সাধ জেগেছিল ঠিকই। ঝাঁকা ভর্তি হরেক রকমের, হরেক নামের আম নিয়ে ফেরিওয়ালা। বিচিত্র সুরে স্ব-স্ব পণ্যের রূপগুণের বর্ণনা দিচ্ছে। ডাব-নারিকেলও আছে। এক রুপিতে চারটে বড় আকারের আম। আমাদের এখানে যে গুলিকে মালদই আম বলা হয় এরকমই তবে নাম ভিন্ন, স্বাদ আর মিষ্টিও বেশি। আমের স্বাদে ইলিশ ভাজার বাসনা উবে গেল।
আসাম ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় ঢুকে গেছি ঘণ্টা কয়েক আগেই। সকল বিস্ময় অতিক্রম করে, অপার কৌতূহলে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ফেরির বেঞ্চে বসে আছেন তিন-চারজন বীর পুঙ্গব। কুকুর বাঁধার শিকলের মতো চার-পাঁচ ফুট দীর্ঘ শিকল দিয়ে কোমরের সাথে রাইফেল বাঁধা। নকশালরা কখন ছিনিয়ে নেয় এই আতঙ্কে রাইফেল পুলিশের এমন যুগল বন্দিত্ব। বিপ্লবের নামে পশ্চিমবাংলাজুড়ে চলছে খতমের রাজনীতি। রাজনীতি তো নয় খুনোখুনির মাতম। কে কোন দিকে কখন খুন হচ্ছে তার ঠিক নেই। জোতদার, মুনাফাখোর, বর্জুয়া, পেটিবর্জুয়া, রাজনীতিবিদ, পুলিশ টার্গেট এদের। মাঝে মাঝে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়, নিজেরাও মরে। প্রতিদিন গড়ে তিনজন পুলিশ খুন। খুন হোক, কিন্তু অস্ত্র যাতে সহজে নকশালদের হাতে না পড়ে সেটি নিশ্চিত করতেই এই বন্ধন। ফেরি পেরিয়ে আবার ট্রেন। এবার ইস্টার্ন রেলওয়ে। রেল লাইনের দু’ধারে সারি সারি আম গাছ। ধানক্ষেতের আল ধরেও আমগাছের সারি। ফলভারে বৃক্ষশাখা আভূমি নত হয়ে আছে। স্টেশনের প্লাটফর্মগুলিতে ভিড় করে আছে শরণার্থীর দল। কেউ গাড়িতে উঠবে আবার কেউ অস্থায়ী আবাস বানিয়ে তিন টুকরো ইটের চুলায় হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। হিমালয় থেকে সুন্দরবন, পঞ্চগড় থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সীমানা। যে যে দিকে পারছে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা Ñ সীমান্তের এই জেলাগুলির আশ্রয় শিবিরে আর ঠাঁই নেই। স্কুল, কলেজ, রেলস্টেশন, পরিত্যক্ত বাড়ি, খালি গুদামঘরে এসে জড়ো হচ্ছে ছিন্নমূল মানুষের দল। ভিড়ের ফাঁকে স্টেশনের দেয়ালে বিশাল আকারের লেখা নজরে পড়েÑ বর্ধমানে জোতদারদের গলাকাটা চলছে চলবে। দা-মনির বর্তমান কর্মস্থল বর্ধমান। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বর্ধমানে নয়, আমরা কলকাতা থাকব। মফস্বলের দরিদ্র অনুন্নত এলাকা বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে নগর কলকাতায়ও বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে গেছে তীব্রভাবে। তবুও রাজধানী বলে কথা। পুলিশ, সিআরপি (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ), মেট্রোপলিটন পুলিশের অভাব নেই। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভাবা যায়। (চলবে)