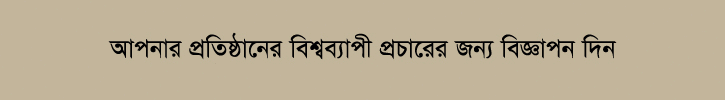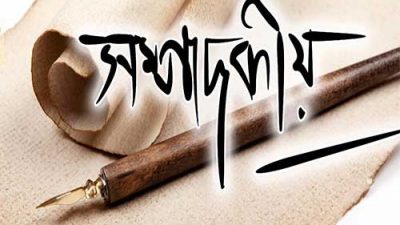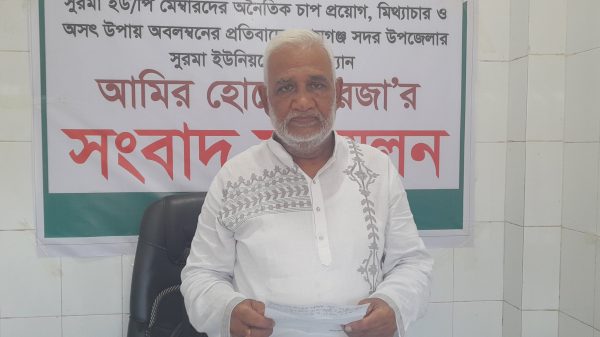ঝরাপাতার পান্ডুলিপি : শরর্ণাথী ৭১
- আপডেট সময় মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬
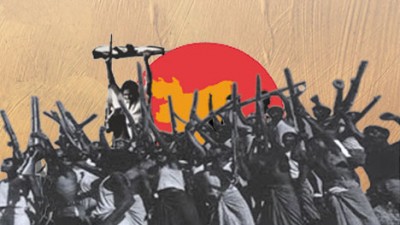
সুখেন্দু সেন ::
(পূর্ব প্রকাশের পর)
জেঠামশাইরা বালাটের লালপানি থেকে চলে এসেছেন করিমগঞ্জে। বাবা আগের মতো একই কারণে এলেন না। সরল যুক্তি, এদের ক্যাম্পে রেখে কি করে যাই?
আমাদের এক কাকার পরিবার তখনও বালাট শরণার্থী শিবিরে। তাই তাদের সঙ্গেই বালাট ক্যাম্পে রয়েগেছেন। খবর পেয়ে করিমগঞ্জ এলাম। শিলচর থেকে ট্রেনে করিমগঞ্জ। জয়বাংলার লোকদের টিকেট লাগে না। অনেক সময় শরণার্থী কার্ড, ক্যাম্পের কাগজপত্রও দেখাতে হয় না। ক্যারোলিন শার্ট, সুইস ঘড়ি, পারুমা জুতা ওপাড়ের লোকদের পরিচয় নিশ্চিত করে দেয় আগেভাগেই। এ মৌসুমে শহুরে লোকদের পায়ে রাবারের পাম্পসু পারুমা নেই, তবে গায়ে ক্যারোলিন শার্ট আছে। বুক পকেটে পাইলট, ইয়ুথ, উইংসাং ফাউন্টেন পেনও নজর কাড়ে। আবার রুক্ষ, শুষ্ক চেহারার মলিনবেশী নারী-পুরষ, শিশু, বৃদ্ধের দলবেঁধে উদ্ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটিতে বুঝা যায় সদ্য আগত শরণার্থী। সরাসরি পাঞ্জাবির আক্রমণ থেকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসা লোকদের আচরণ দাবানলে আক্রান্ত প্রাণীর মতো, ভীত সন্ত্রস্ত। আপ-ডাউন দু’দিকের ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রী জয়বাংলার। কেউ একাকী এদিক সেদিক ঘুরছে। কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে। কেউ দলবেঁধে জিনিসপত্র বুচকা-বুচকি নিয়ে আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি করছে।
মহকুমা শহর করিমগঞ্জ, অনেকটা সুনামগঞ্জের মতোই। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, খাবার-দাবার, আপ্যায়ন, বাড়ি-ঘর সবকিছুই সিলেটি সংস্কৃতির অবিকল প্রতিরূপ। সুনামগঞ্জের মতো ঘরে ঘরে বাটা ভরা পান প্রাথমিক আপ্যায়নের অনিবার্য অনুষঙ্গ। করিমগঞ্জের রিকশায় বেল নেই, পথচারীদের সচকিত করে পেপ্ পেপ্ করে ভেঁপু বাজে। টেক্সির চলাচল আছে। আছে টেক্সিস্ট্যান্ড। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কুশিয়ারা সীমান্ত রেখা হয়ে পৃথক করে রেখেছে দু’দেশকে। স্বাভাবিক অবস্থায় দু’পাড়ের যাতায়াতে নদী তেমন বাধা নয়। সীমান্তের অচলায়তন টপকে জকিগঞ্জের রিকশা চালক, দিনমজুর এপাড়ের করিমগঞ্জ শহরে এসে রিকশা চালায়, কাজ করে। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। জকিগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের চলাচল চোখে পড়ে। লোকজন ধরে এনে নদীর পাড় ঘেঁষে তৈরি করছে বাংকার। চাঁদতারা পতাকা নিয়ে মিছিলও বের হয়। ‘নারায়ে তাকবির – আল্লাহু আকবার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ শোনা যায় শহর থেকে। মাঝে মাঝে এপাড়েও এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। বদরপুরে ভারতীয় ভূখন্ডে কারা যেন পাকিস্তানি পতাকা তুলে দিয়েছিল একদিন। একই ধরনের স্লোগান দিয়ে মিছিলও হয়েছিল। এ নিয়ে দিনভর উত্তেজনা। পুলিশ এসে সামাল দেয়। দেশ ভাগাভাগিকালে পুরো কাছাড়ই নাকি পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। পুরো জেলা না হোক হাইলাকান্দি, বদরপুর, করিমগঞ্জ তো অবশ্যই। যদিও আসামের অনেক মুসলিম নেতা, কংগ্রেসের মঈনুল হক চৌধুরী, ফরখর উদ্দিন আলী আহমদ এমনকি মুসলীম লীগ নেতা সাদ উল্লাহও পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না। সিলেট মোগলাবাজারের আদিবাসিন্দা মওলানা মো. আব্দুল জলিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা, এখানকার লোকসভার সদস্য। ’৪৭ এ পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আর পাকিস্তানেই থাকেন নি। ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণকালে কেন জানি রেডক্লিফের পেন্সিল কুশিয়ারার বাঁকের সাথে মিলে গিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই থানাগুলিকে ভারতে রেখে মৌলভীবাজারের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, কমলগঞ্জকে পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দাগ টেনে দেয়। সেই বঞ্চনার ক্ষত এখনও রয়ে গেছে। ’৪৭-এর পর কাছাড়ের অনেক মুসলিম পরিবার দেশত্যাগ করে সিলেটে পাড়ি দিয়েছিলেন। উদ্বাস্তু হলেও সেখানকার রাজনীতি, আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রয়েছে তাদের। এদের অনেক এবার শরণার্থী নাম লিখিয়ে জন্মভূমে পরদেশী হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। অনেকের অবশ্য নিজের বাড়িঘর রয়ে গেছে। কেউ কেউ ‘মুক্তি’ হয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেছে। কিন্তু এখানকার আদি কট্টরপন্থি অনেকেই পার্শ¦বর্তী পাকিস্তানকে ভরসার স্থল মনে করে সেদেশ ভেঙে যাক, তা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই জয়বাংলার সমর্থকদের প্রতিও কট্টরপন্থিদের চাপা অসন্তোষ।
করিমগঞ্জ শহরের প্রায় সকল স্কুল কলেজই শরণার্থীতে ঠাসা। বিরজাসুন্দরী হাইস্কুল, বিপিন পাল স্কুল, ভিকম চাঁন্দ হাইস্কুলে সিলেট শহরের অনেক হিন্দু মুসলিম পরিবারের আশ্রয়, মণিপুরী পরিবারও আছে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও আশ্রয় জুটেছে অনেকের। হিন্দি স্কুলে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আস্তানা। বরুণ রায়, নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, গোলজার আহমদরা এখানে অবস্থান করছেন। পার্টির ছেলেদের তাদের লাইনে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছেন। ট্রেনিংয়ে পাঠানোর চেষ্টাও চলছে। আওয়ামী লীগ নেতা ফরিদ গাজী এমএনএ করিমগঞ্জে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন। তবে নিয়মিত ছোটাছুটি করছেন শিলচর, শিলং, ধর্মনগর। বৈঠক করছেন মাছিমপুর ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে। সিলেট শহরের অনেক পরিবারই বাসা ভাড়া করে আছেন লন্ডনি স্বজনদের কল্যাণে। প্রবাসীরা মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে সার্বিক সহায়তা দিয়েছেন তেমনি শুধু নিকট আত্মীয়রাই নয় ছিটেফোটা আত্মীয়তায়ও পাউন্ডের সমর্থন মিলেছে। তাই অনেকেই আরাম-আয়েশে থাকতে পেরেছেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতাদের আস্তানা গৌরী হোটেল। বেলা রেস্টুরেন্ট সরগরম সিলেটি আড্ডায়।
বাঙালি মেজর সি.আর. দত্ত করিমগঞ্জে এসে শরণার্থী শিবির ঘুরে মুক্তিবাহিনীর জন্য লোক বাছাই করছেন। যে কোনো দিন ডাক পড়বে, ট্রেনিংয়ে যেতে হবে আগরতলার কাছাকাছি কোন গোপনস্থানে। কারোর অধীর প্রতিক্ষা কখন ডাক আসবে। আবার কেউ সময় মতো নানা ছুতোয় কেটেও পড়েছে। তবে এগিয়ে চলছে সামরিক প্রস্তুতি। সংগ্রাম পরিষদের নেতারা, এমএনএ, এমপিএ’রা মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে অস্ত্র, গোলাবারুদ, প্রশিক্ষণের জন্য আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশ্বাসও পাওয়া যাচ্ছে। বুঝা যায় এবার রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হবে। তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে উঠা বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত প্রতিরোধ যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিছু হটতে হয়েছে বাঙালিদের। এখন যুদ্ধ কেবল প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই। এবার জয়ের জন্য লড়াই। এদিকে সীমান্তের কাছাকাছি শত্রুবাহিনীর উপস্থিতি থাকায় সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। রাতে কামানের গোলা, মর্টার শেলের দ্রিম-দ্রাম আওয়াজ শোনা যায়। করিমগঞ্জবাসীও এ শব্দে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোন গোলাটি ‘মুক্তির’ আর কোনটি পাঞ্জাবির সেটি আন্দাজ করে নিতে পারে।
মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনী এখানে শুধু ‘মুক্তি’ নামেই পরিচিত। বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দ এর মধ্যে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি, বালুচ, পাখতুন, সিন্ধি এমনকি বাঙালি থাকলেও পাকিস্তান সেনাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাঞ্জাবি নামে অভিহিত করা হয়। মার্চের প্রথম প্রতিরোধ থেকেই পাঞ্জাবি শব্দের ব্যাপক প্রচলন এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত শরণার্থী এবং অবরুদ্ধ বাঙালি মাত্রেই আতঙ্ক, ভয় এবং ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করেছে এই শব্দটি। ভারতীয়রা কখনো পাঞ্জাবি বলতো না। এদেশেও পাঞ্জাব রাজ্য রয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয় পাঞ্জাবের অধিবাসী। তাই এখানে পাকিস্তানি বাহিনী, পাকসেনা, খানসেনা আবার কখনো সংক্ষেপে শুধু পাকি। পাকিস্তান নামের পরিবর্তে তখনও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লোকমুখে জয়বাংলার প্রচলনই বেশি। সীমান্তে যেখানে পাকিস্তান বাজার সেটি জয়বাংলা বাজার। স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ সকল শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনা এক শব্দে ধারণ করে রেখেছে ‘সংগ্রাম’। মহাকালের এক অবিনশ্বর স্মারক, অমলিন যুগচিহ্ন। সময়, স্মৃতি আর অনুভবকে ভাগ করে নিয়েছে এভাবেইÑ সংগ্রামের আগে, সংগ্রামের পরে এবং সংগ্রামের বছর বা সংগ্রামের সময়।
করিমগঞ্জের শরণার্থী শিবিরে অনেক বিপর্যস্ত-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দেখা মিলে। ২৬ মার্চেই সিলেটে পাঞ্জাবিদের আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। ২৭ মার্চ সকাল থেকে নিম্বার্ক আশ্রম, মীর্জাজাঙ্গাল এলাকায় ২৭টি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। অবস্থাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়ি তল্লাশী করে অনেককে ধরে নিয়ে যায় পাকসেনারা। ৪ এপ্রিল জিন্দাবাজার ন্যাশনাল ব্যাংক পাহারায় নিয়োজিত ৯জন বাঙালি পুলিশকে একই সঙ্গে হত্যা করে। মেডিকেল কলেজ আক্রমণ করে ডা. শামসুদ্দিনসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। শহরতলির তারাপুর বাগান, খাদিমনগর, কালাগুলেও চলে নির্মম হত্যাকান্ড, ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে থানা সদরে। সড়ক যোগাযোগ থাকায় সহজেই পাঞ্জাবিরা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। গোলাপগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ থানার রাস্তার পাশের গ্রামগুলি আক্রান্ত হয়। নিরাপদ ভেবে শহরের অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। আক্রমণের ভয়ে পলায়নপর নিরীহ নারী-পুরুষও রক্ষা পায়নি। নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য, আবার কোথাও নির্যাতনের শিকার হয়ে এপ্রিলের প্রথম থেকেই সিলেট অঞ্চলের লোকজন সীমান্ত পেরিয়ে আসতে শুরু করে। চারখাই-এ সীমান্তমুখী শরণার্থী দলের উপর বিমান আক্রমণ চালানো হলে হতাহত হয় কয়েকজন। সীমান্তের কাছাকাছি হলেও দেশত্যাগের প্রস্তুতি নেয়ার আগেই বিয়ানীবাজারের সুপাতলা গ্রামে গণহত্যা চালিয়ে মনোরঞ্জন ঘোষের এক পরিবারেরই ১৩ জনকে হত্যা করে পাঞ্জাবিরা। (চলবে)