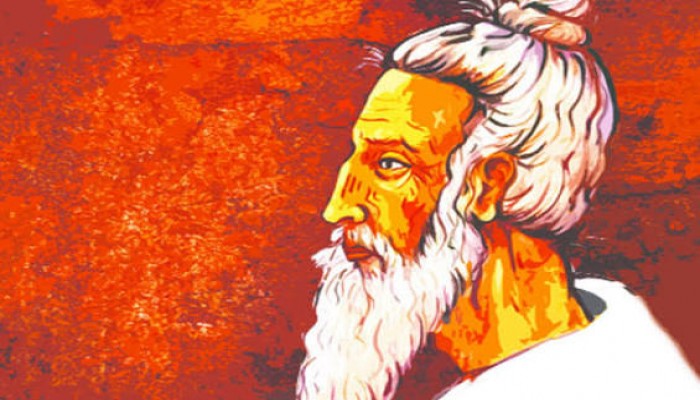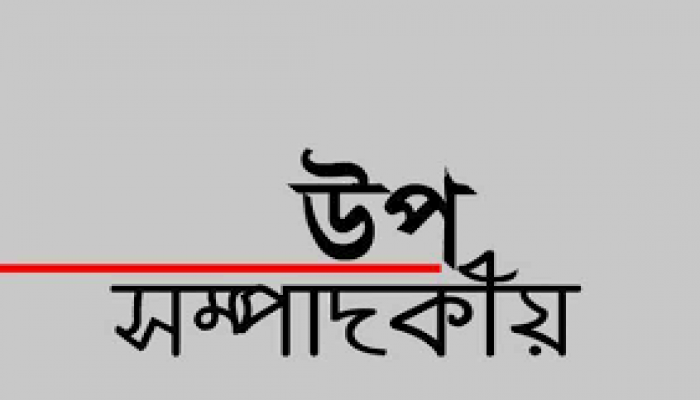বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি কৃষকদের নিয়ে ভাবতেন এবং কৃষকদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করতেন। আধুনিক কৃষিকাজের মাধ্যমে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের মানোন্নয়নের জন্য তিনি কখনও শিলাইদহ, কখনও পতিসর কিংবা শ্রীনিকেতনকে বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে গবেষকরা নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান করে চলেছেন। কৃষিকাজেও বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর। গবেষণায় দেখা গেছে কৃষিকাজে জোর দিতেন তিনি। তাঁর সেই আগ্রহ ও ভালোবাসারই ফসল বোলপুরের শ্রীনিকেতন। কৃষক ও গৃহপালিত পশুর জন্য তিনি যা করেছেন তার সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীনিকেতনে। এখানে কৃষিবিজ্ঞান ও প্রাণী বিজ্ঞান পড়ানোর সাথে সাথে হাতেকলমে চর্চাও হয়। বিজলী পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি বসুকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আমি দেশের জন্য কী করেছি তা হলে পরলোক থেকে আমার উত্তর হবে শ্রীনিকেতন। যে দেশে মানুষ দু-মুঠো অন্নের জন্য কাঙাল, সেখানে তাঁর কর্তব্য কী? তারা যাতে দু-মুঠো খেতে পায়- তাঁর জন্য আমার আয়োজন শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হলেই একজন শহুরে মানুষ যেভাবে মেতে ওঠেন, সেভাবে গ্রাম বাংলার একজন কৃষক মেতে ওঠেন না। কারণ আজও গ্রাম বাংলার কৃষক তাঁর স¤পর্কে ততটা জানেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বীরভূমের শ্রীনিকেতনে এগ্রিকালচার, ডেইরি, পোল্ট্রি, ফিসারি, পটারি, কটেজ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজে নিজের জীবনের একটা বড় অংশ ও সময় দিয়ে গেছেন তা তাঁরা জানেন না। সমীর শীলের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের কৃষিবিষয়ক ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৫-০৬ সালে আমেরিকা থেকে সবুজ গো-খাদ্যের বীজ আনিয়ে শিলাইদহে প্রথম বাঙালি হিসেবে উন্নত গো-খাদ্য বা সবুজ ঘাস চাষ করেন রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরুর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে দুধের জন্য ডেইরি বসানো হয়। এছাড়া উন্নত প্রজাতির গাভি, বলদ ও মুরগী বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন তিনি। ১৯২২ সালে ডেইরি স্থাপিত হয় শ্রীনিকেতনে। হাল টানার জন্য কঙ্করেজ প্রজাতির বলদ ও দুধের জন্য রেড সিন্ধ্রি প্রজাতির গাভি আনা হয়। এরপর শ্রীনিকেতনে পোল্ট্রিও স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে ডিমের জন্য লেগ হর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড এবং ব্ল্যাক মিনর্কা প্রজাতির মুরগী আনা হয় ঊনবিংশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির পড়াশোনা মানেই বিদেশে গিয়ে ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারি পড়া। কিন্তু সেই আমলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও কনিষ্ঠ জামাতাকে পাঠান কৃষিবিদ্যা পড়াতে। ১৯৪১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানব সমাজের উন্নতির কথা ভেবেই গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তার একক প্রয়াসে (১৮৯৯-১৯০৬) শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন জমিতে নতুন ধরনের ধান চাষ, আমেরিকান ভুট্টা, নৈনিতাল ও আমরাগাছি আলুর চাষ, পাটনাই মটর, আখ, কপি, রাজশাহীতে রেশমচাষের চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফল হন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন নিজের অর্থ ব্যয় করে কৃষকদের উন্নয়নে। ১৯০৫ সালে শিলাইদহে ও পতিসরে চাষিদের ঋণ পাওয়া যাতে সহজসাধ্য হয় সেজন্য কৃষিব্যাংক গঠন করা হয়। কৃষিকাজকে আরো সহজ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো-পালন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার এক বছর পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও ওই একই বিষয় শিক্ষালাভ করার জন্য আমেরিকায় পাঠান। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে কৃষি খামার ও সঙ্গে কৃষি বিষয়ক নানা ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগার গড়ে তোলেন। এরপর ১৯০৮ বিরাহিমপুর পরগণায় শিলাইদহে ভগ্নদশা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে গ্রামের লোকেদের নিয়ে তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেন। এই কাজে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে যোগদান করেন কালীমোহন ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ও অন্যান্যরা। ১৯১৫-১৯৪০ সালে পতিসরকে কেন্দ্র করে কালিগ্রাম পরগণায় গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ নতুন করে শুরু হয়। সহযোগী হিসেবে যোগ দেন বাগনান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুল সেন, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বেশর বসু, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, নলিনী বসু, ভুপেশচন্দ্র রায়, রতিকান্ত দাস, সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কর্মীরা। পতিসরে মন্ডলী প্রথা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং একে ভিত্তি করেই গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়। এলাকার শক্ত এঁটেল মাটি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ গ্রামের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, বয়ন ও মৃৎশিল্পের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কোয়া নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, ধর্মগোলা ও ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদান, সালিশি বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন, দু’শটি প্রাথমিক স্কুল, পতিসরে হাইস্কুল, তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপন ইত্যাদি নানা গ্রামোন্নয়নের কাজ করা হয়। নিজে চাষিদের অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিজনিত ফসলের ক্ষতি হলে তাদের দেয় খাজনা মওকুফ করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। কিন্তু সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ১৯০৫ সালেই তিনি পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। এই ব্যাংকের মূলধন বরীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার করে জোগাড় করেন। এ ছাড়া বিশ্বভারতী হাসপাতাল ফান্ড ও টিউবওয়েল ফান্ডের টাকা সেখানে জমা রেখে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে চাষিদের কাছে অধিক পরিমাণে টাকা জোগান দেওয়ার মতো প্রচেষ্টা করা হয়। পরে নোবেল পুরস্কার পাওয়া ৮২,০০০ টাকা পতিসরের ব্যাংকে রেখে মূলধনের সমস্যার সমাধান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক জীবনে কেবল একজন প্রজাবান্ধব জমিদার ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে যে সুপরিচিত ছিলেন তা কিন্তু নয় বরং আধুনিক কৃষির একজন রূপকার হিসেবেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয়। গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও দুস্থ কৃষকের মাঝ থেকে কবিগুরু খুঁজে পেয়েছিলেন উপেনের চরিত্র, লিখেছিলেন কালজয়ী কবিতা ২ বিঘা জমি। মহাজন, জমিদারদের কবল থেকে এসব উপেনদের বাঁচাতে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণের কথা ভেবেছিলেন তিনি। আধুনিক কৃষির রূপকার হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় কৃষকের দোরগোড়ায় আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি ভেবেছিলেন গভীরভাবে। ভারতের শান্তি নিকেতন এবং বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের শাহবাজপুর, কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহে তিনি বনবীথি, ছায়াবীথি, ফলবীথি গড়ে তুলেছিলেন সেটি ছিল অভাবনীয়। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতের, বর্ণের, রঙের নানা রকম গাছ-গাছড়ার যে সংগ্রহশালা গড়েছিলেন তা আজকের দিনের পরিকল্পিত সমৃদ্ধ বোটানিকেল গার্ডেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া জমিতে জৈবসার ব্যবহার, মানসম্মত বীজ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা, জমির আইলে তথা পতিত জমি ব্যবহারে কৃষি ফলন বাড়ানো - তার পরিকল্পনা থেকে আসে। রবীন্দ্র সময় থেকে এ যাবৎ বিশ্বখ্যাত একজন মানুষ কৃষির বাইরের লোক হয়েও এত বেশি কাজ করেছেন এমন রেকর্ড কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই আছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মতো অন্য কোন সাহিত্যিক ভাবেননি।
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক, পূর্ব নতুনপাড়া, সুনামগঞ্জ।
নিউজটি আপডেট করেছেন : SunamKantha
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃষি ভাবনা: এস ডি সুব্রত
- আপলোড সময় : ০৭-০৮-২০২৫ ০৮:০৬:০১ পূর্বাহ্ন
- আপডেট সময় : ০৭-০৮-২০২৫ ০৮:০৬:৩১ পূর্বাহ্ন

কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ
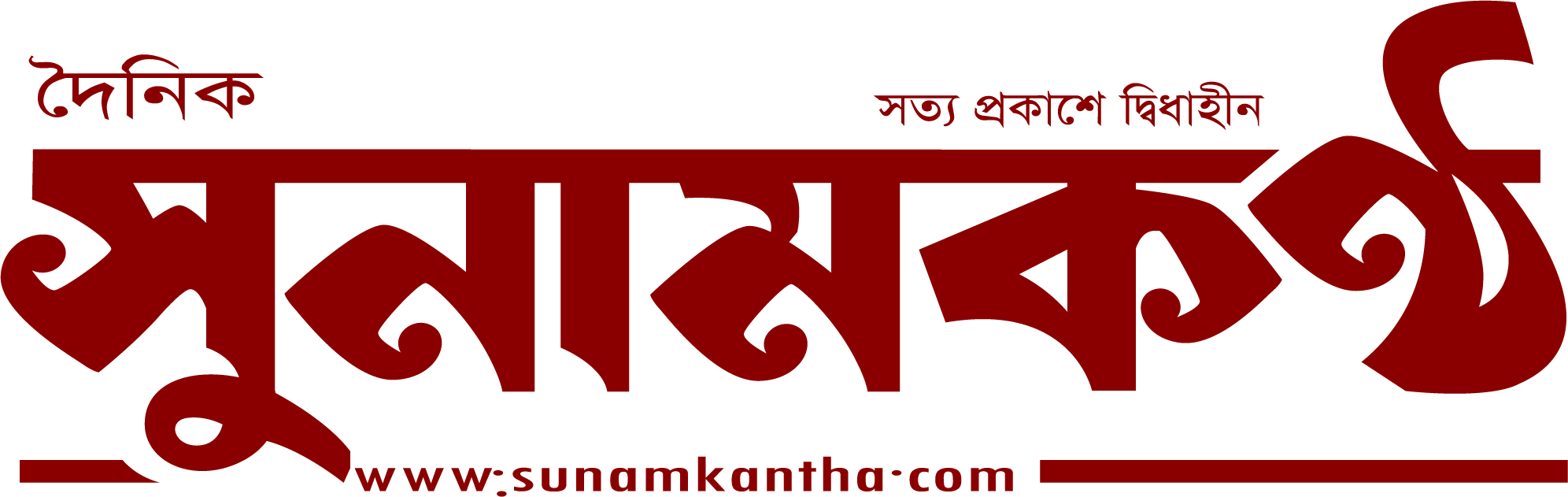
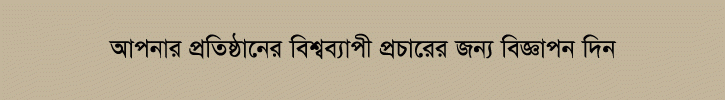

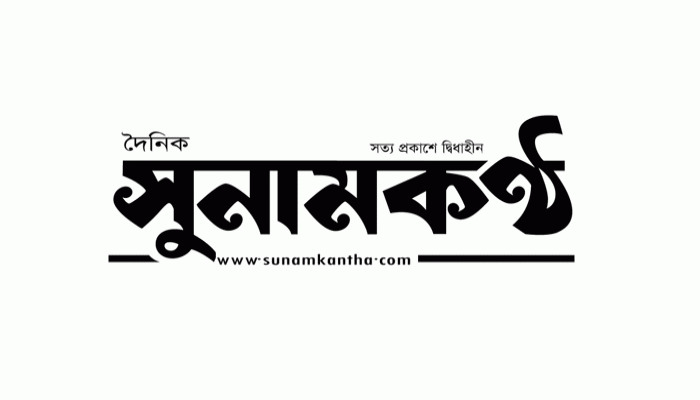 সুনামকন্ঠ ডেস্ক
সুনামকন্ঠ ডেস্ক