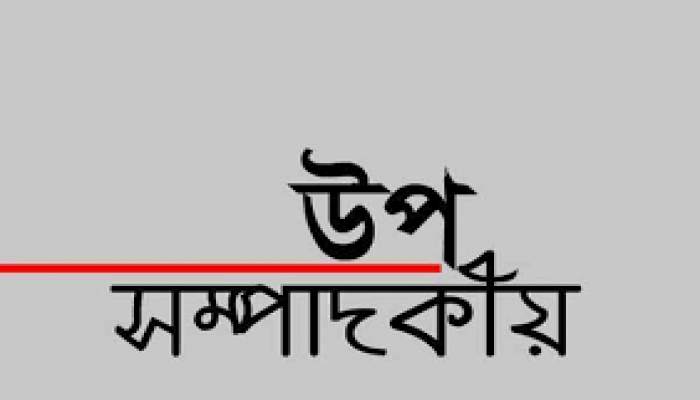সুশান্ত দাস::
ধান মাড়াই হলো ধান উত্তোলন প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ ধাপ। হাওরাঞ্চলের বৈশাখের এক পরিচিত শব্দ। কাটা ধানগাছ হতে ধানকে ছাড়ানোর নাম। বাংলা একাডেমি অভিধানে ‘মাড়া’ শব্দ দিয়ে মর্দন করা/পেষণ করা আর ‘মাড়াই’ শব্দ দিয়ে মাড়ানোর কাজ উল্লেখ থাকলেও ভাটির হাওরে ধান ‘মাড়াই’ এর চেয়ে ‘মাড়া’ নামেই অধিক পরিচিত। মাড়াই এর সংজ্ঞা খোঁজতে চোখে পড়ে “যে পদ্ধতিতে দানাজাতীয় ফসলের ভোজ্য অংশ (দানাশস্য, যেমন- ধান, গম প্রভৃতি) থেকে ফসল উদ্ভিদের অন্যান্য অংশকে আলাদা করা হয়, তাকে মাড়াই বা থ্রেসিং বলে।” গরু বা মহিষকে কাটা ফসলের উপর দিয়ে মাড়াই করে অথবা থ্রেসার নামক যন্ত্র ব্যবহার করে হাতে মাড়াই করা যেতে পারে। মানুষের দীর্ঘ চিন্তা ও বিজ্ঞানের বদান্যতায়, বর্তমানে ধান মাড়া দেয়া, মেশিন নির্ভর। আমাদের ছোটবেলায় দেখা, মেশিন নির্ভর নয়; ছিল গরু নির্ভর। ক্বিত্তার ক্বিত্তার জমির মাড়া দেওয়া হতো গরু দিয়ে। হাওরের হাওর, জমির ধান মাড়া হতো গরু দিয়ে। সাতক্ষেইরা, দশক্ষেইরা, আটারোক্ষেইরা, লোঙ্গার পর লোঙ্গা এমন জমিনের মাড়া হতো দুইদিন, তিনদিন হতে চারদিন; পাঁচদিন পর্যন্ত চলতো। এমনও হতো একটু দূরের হাওর হলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত মাড়া চলতো। বাঁশ বেতের দাঁড়া দিয়ে হুড়া (অস্থায়ী ঘর) বানিয়ে থাকা হতো। হঠাৎ করে কালবৈশাখী ঝড়ের তা-বে খড়ের লাছিতে (শুকনো খরের গোলাকৃতি স্তূপ) জায়গা করে নেয়া হতো। বস্তায় বস্তায় ধান ভরে, বেশি হলে গোলি ধানের স্তূপ বানিয়ে, একেবারে মাড়া কাজ শেষ করে ধান খলাতে পাঠানো হতো। হাওরের অবস্থান বুঝে অনেকে নৌকা, গরুর গাড়ি, হল্লা এসব ব্যবহার করতো। সিংহভাগই গরুর গাড়ি ব্যবহার করতো। আশি নব্বই দশকেও দেখাযেতো, গ্রামের ছোট ছোট কৃষক মিলে গড়ে তোলে মাড়ার সঙ্গ (দল)। গ্রাম্য জনজীবনের কাছে ‘মাড়ার হঙ’ হিসেবে ছিল পরিচিত। বিবেচনা করা হতো কে বা কার, কতোটুকু জমি চাষ, কতোটি গরু, মাড়া কর্ম সাধনে কতোজন লোকবল। আরো দেখা হতো জমির অবস্থান (দূরের, কাছের), দেশি ও বিদেশি ধানের ধরণ। সাব্যস্ত করা হতো মাড়া চক্করের জন্য দাঁড়া, খড় (ক্ষের) ও ধান বহনের জন্য গরুর গাড়ি, হল্লা, জোয়াল, গরুর গাড়ির জন্য শক্তিশালী বলদ, ষাঁড়, শক্তিশালী গাভী। সিদ্ধান্ত নেয়া হতো ফাঁগা, কাঁচি, ডাবা-আইল্যা, লাইঙলা এমনসব তৈজসপত্রের। তবে কোন কোন গ্রামে মহিষের প্রচলন চোখে পড়তো। ধান মাড়া নির্ভর করে ধান পাকা ও কাটার উপর। সঙ্গের মধ্যে যাদের আগে কাটা হয়েছে তাদের; আবার একতরফা ভাবে শুধু যে এক পক্ষের তাও নয়। বৎসরের পরিস্থিতি, জমির অবস্থান (দূরের ও কাছের হাওর), জমির পরিমাণ ও ধান কাটাকে প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত প্রত্যুষে মাড়া দেওয়ার জন্য বাড়ি হতে যাওয়া হয়। ভোরের তারা কিংবা ভোরের ফিঙে (প্যাছকোন্দা) পাখির ডাককে লক্ষ করে ঘুম ভাঙানোর ডাকাডাকি শুরু হয়। প্রতিযোগিতা শুরু হয় কার আগে কে হাওরে পৌঁছাবে। কার আগে কে মাড়া শুরু করবে। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাড়ার সঙ্গীদের বাড়ি হতে লামাতে গরু জড়ো করা হবে। সময় অপচয় রোধ করতে, জোয়ালের সাথে লাইঙলা (তুলনামূলক মোটা দড়ি), বেঁধে রাখা হবে। বড় বলদ/ষাঁড় দিয়ে গরুর গাড়ি জোড়া হবে। মাড়া চক্করের জন্য সংগে বাঁশ বেতের দাঁড়ার বুন্দা নিয়ে যাওয়া হবে। কোন একজনের দায়িত্বে মাড়ার জন্য গরু নিয়ে যেতে হবে। বাদ বাকিদের মধ্য হতে স্ব স্ব দায়িত্বে মাড়ার আনুসাঙ্গিক পত্র যেমন- ফাঁগা, কাঁচি, ডাবা-আইল্ল্যা নিতে হবে। প্রয়োজনে অতি তাপমাত্রায় পানি পিপাসার জন্য কলসী ভরে খাবার পানি নিতে হবে। ধান মাড়ার সময় বৈশাখকে সুবৈশাখী ও কুবৈশাখী হিসেবে অবিহিত করা হয়। নির্দিষ্ট করে বৈশাখের বৈশাখী হলেও ধান মাড়া অনেক সময় চৈত্রের শেষ হতে, কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠের কিছু দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। অনেকে অতি বৃষ্টির কারণে ডগরারবছর আবার অনেকে কাঁচাইরার বছরও বলে থাকেন। তখন অতি বৃষ্টিতে ধান পাকতে সময় নেয়। তুলনামূলক নিচু, বিল-ঘেষা জমির ধান পানিতে হাবুডুবু খায়। তুলনামূলক খরা থাকলে আবহাওয়া ভাল বলেই ধরা হয়। বলা হয়ে থাকে সুবৈশাখ। তখন বাড়ির উঠান, খলা, মাঠ-ঘাট, হাওর লামায় সর্বত্র মানুষ বিরাজ করে। অনেক সময় গরু পালও ঘাস খেতে খেতে হাওরে থেকে যায়। দুধ দোহনের জন্য গাভীকে খোঁজে আনতে হয়। জন জীবনে আনন্দের সীমা থাকে না। কান পেতে রাখলে কানে বাজে বিলে আটকে থাকা জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, রাতের রূপালী চাঁদ ও পাকা ধানের শীষ কিংবা কান্দার চাইল্ল্যা ঘাসের শীষ মিশ্রিত লোকজীবন, পল্লী জীবনের রূপকথার সুর। তবে আবহাওয়া বৈরী হলে কানে বাজে আনন্দ বিধুরের সুর। কষ্টের থাকে না অন্ত। নগরজীবনের পিচ ঢালা রাস্তার ন্যায় হাওরের বুকচিরে গুপাট নামক কাঁচা রাস্তাগুলো হয়ে ওঠে কাদাময়। গরুর গাড়ি চলতে ঘটে বেঘাত। মাড়া দিতে গিয়ে বাঁধতে হয় হুড়া (টেম্পোরারি ঘর)। খরকুটো শুকাতে ভোগতে হয়। খলায় জমে যায় স্তূপের স্তূপ গোলি ধানের ঢেরী। লোক মুখেই নিসৃত হয় কাচাঁইরা বছর। পাকা ধান কেটে চার-পাঁচ মুটি করে একেক আঁটি বাঁধা হয়। এসব আঁটিকে আঞ্চলিক ভাষায় মুইট, মুইট্টা হিসেবে বলতে শোনা যায়। ধান কাটার পর এসব মুইট্টাকে টেনে শ্বার্শবর্তী উঁচু কান্দা বা জাঙ্গালে তোলা হয়। তুলনামূলক উঁচু জায়গা লক্ষ্য রাখা হয়; যেখানে ধান ‘মাড়ার চক্কর’ দিতে সুবিধা হয় এবং বৃষ্টি হলেও যাহাতে পানি না জমা হয়। বৃষ্টির পানি হতে পঁচা ও ছুঁটা গরু হতে রক্ষার জন্য কাটা ধানের এসব মুইট্টাকে দুই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। একটি হলো গাইলা (গাইল এর ন্যায় স্তূপাকৃতি) আর অন্যটি হলো লম্বা চতুষ্কোণাকৃতির ‘পাড়া’। কৃষি কাজের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও লিপিবদ্ধকারে ভাটির হাওরের ‘ধান-মাড়া’ নামক এমন কর্মটির আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান তেমন কোন কর্ম এখনো চোখে পড়েনি। জানাযায় ছোট সঙ্গ (দল) বিশিষ্ট ‘ধান মাড়া’ করা হয়ে থাকে ৯টি দাঁড়া দিয়ে তৈরি চক্কর ও এক হাঞ্জুর গরু (৪/৫) দিয়ে। ১৬টি দাঁড়ার চক্কর দুই হাঞ্জুর গরু (৪/১০) দিয়ে। ২৫টি দাঁড়ার চক্কর দুই হাঞ্জুর গরু (১২/১৪) দিয়ে ধান ‘মাড়া’ হয়ে থাকে। চক্করের কেন্দ্র বা হাঞ্জুরের ভিতরের দিকের গরুকে ‘মেইয়া’ আর বাহিরের দিকের গরুকে ‘ধাপা’ বলে। সাধারণত অপেক্ষাকৃত বড়, বয়স্ক, হৃষ্ট-পুষ্ট ও সমজদার কেন্দ্রের দিকের গরুকে “মেইয়া” আর অপেক্ষাকৃত ছোট, চালাক ও চতুর গরুকে ”ধাপা” হিসেবে হাঞ্জুরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্ষেতের আশ-পাশে অপেক্ষাকৃত উঁচু টেক, উঁচু কান্দা দেখে ধান মাড়ার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। খড় শুকানোর জন্য যথেষ্ট জায়গার ব্যবস্থা মাথায় রাখতে হয়। সাধারণত সূর্য উদয়ের আগে হাওরে পৌঁছেই মাড়ার চক্কর বিছিয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়। অনেক সময় বড় মাড়া হলে আগের দিন সন্ধ্যায় মাড়ার জন্য মুইট্টা চক্করে সাজানো হয়। মুইট্টা গুলো চক্করের চতুর্দিকে সাজাতে যেন এক-শিল্পের প্রয়োগ করা হয়। ধানের ছড়াগুলো ভিতরের দিকদিয়ে একটার উপর আরেকটা রাখতে হয়। বিছানো দাঁড়ার-চক্করের চুতুর্দিক হতে সাজানো-ছড়ানো মুইট্টাগুলো আস্তে আস্তে কাঁচি দিয়ে মুইট্টার বাঁধা অংশটুকু কেটে চক্করের মাঝের অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে পয়লা মাড়ার সময় সর্বশেষ মুইট্টা কেটে মাড়াতে ছড়ানো বা ভাঙ্গার সময় স্তুতির ন্যায় লোকজ প্রবাদের ব্যবহার হয়।
যেমন- আইল লক্ষ্মী দিল বর, ধানে চাউলে ঘর ভর; ধানের নাম মাইট্টা, উঠে ধান ফাইট্টা। কাইমে খাইল,কুঁড়ায় খাইল, মাড়ার সময় আইন্না দিল; পূবত আয়,পশ্চিমত আয়, চারকোণা ভাঙ্গিয়া আয়।
চক্করে গরু প্রবেশ করার জন্য একটু জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়। অতঃপর গরু প্রবেশ করিয়ে ফাগাঁ (গরু বাঁধার রশি) দিয়ে গরুর গলায় বেঁধে হাঞ্জুর (গরুর সমষ্টি/পুঞ্জ) করে গরু ডাকানো শুরু হয়। গরু ডাকানোর সময় গানের মতো নানান সুরেলা কণ্ঠ, লোকজ প্রবাদ ব্যবহার হয়। যেমন- হ্যাই; হ্যাই! হাঁটো; হাঁটো! হাঁটো রে; হাঁটো হাঁটো নানান ভঙ্গিতে নানান সুরে। ব্যবহার করা হয় হ্বলা (বাঁশের তৈরি লাঠি ও মাথায় কুঁতি, ছোট আলপিনের মতো লোহা)। সাধারণত চক্কর শুরু করা হয়ে থাকে ঈশান কোণা ধরে ঘড়ির কাটার দিকে। আর এই ঈশান কোণা হতে ঐ ঘড়ির কাটার উল্টাদিক ধরে মানুষ ‘কাইচ্ছা দেয়’ / কাছাটানে’ (চক্করের মাঝের অংশে মুইট্টায় গরুর পা লেগে চতুর্থদিকে ছড়িয়ে গেলে, এর কিনারা হতে অতিরিক্ত অংশকে টেনে আবার মধ্যবর্তী জায়গায় ফিরিয়ে দেয়া)। এভাবে ধান মাড়াতে প্রথমে কাছাটানা, দ্বিতীয়ত লাড়াদেয়া, তৃতীয়ত তলা ঝাড়া দিয়ে তিনটি ধাপে মাড়া দেওয়া স¤পন্ন হয়। মাড়া বড় হলে একেকটি ধাপকে আবার দুই-তিনবার করেও দেওয়া হয়। বিশেষ করে মাড়া বড় হলে দুই/তিন বার করে লাড়া দিতে হয়। চক্করে ধান জমা শুরু হলে কিংবা মাড়া শেষ হলে নির্দিষ্ট পরিমান করে ধান বস্তায় ভরে বাড়ির খলায় পাঠানো হয়। সেখানে পায়ে পা মিলিয়ে ধান শুকানো হয়। ধান পাঠাতে ও গরুর গাড়ি চালাতে দক্ষ ও গত্ত্বরেজোড় আছে এমন একজনকে গাড়ি পরিবহনে পাঠানো হয়। কারণ মাড়াতে ধান ভরা বস্তা গাড়িতে উঠাতে একে অন্যের সহায়তা করলেও খলাতে বস্তা নামাতে, মাড়া হতে যে নিয়ে যায় তার উপরই নির্ভর করতে হয়। ধান মাড়ার সময় গরু দিয়ে ঘাটানোর ফলে কাটা ধানের ছড়া হতে ধান বিচ্ছিন্ন হলে তাকে ‘গুডা’ হিসেবে আখ্যায়িত করতে শোনা যায়। পয়লা মাড়ার সময়ে “গুডা” আসলে মাড়া হতে একটা ক্ষের (খড়) নিয়ে আংটির ন্যায় “ভাড়াল” বানাতে হয়। উক্ত ভাড়ালটি মেইয়াগরুর (কেন্দ্রের গরু) মাথার বাম পাশের ‘শিং’ এ লাগিয়ে মাড়ার আড়াই ঘুর্ণনের পূর্ণতায় খোলে নিতে হয়। পরে চক্কর বা চকরের ঈশান কোণায় ধানের নীচে রাখতে হয়। ধান মাড়া সম্পর্কে এমনই কথাবার্তা জানাযায়, পঞ্চাশোর্ধ্ব কৃষক নেত্রকোণার খালিয়াজুড়ি উপজেলার কাজল সরকার হতে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানধারী তেমন উচ্চ প্রতিষ্ঠানে যেতে পারিনি তবে বাপদাদা পূর্বপুরুষদের কর্ম দর্শন এবং সেই শৈশব হতে নিজে করে আসা কৃষিকর্ম করার অর্জিত কর্মজ্ঞানে আমরা এভাবেই ধান মাড়া করে ও দেখে আসচ্ছি। আশির দশকে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির শাল্লার অন্যতম কর্মী দুরন্ত দাশ বলেন- হাওরের এক প্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে লোকআনুষ্ঠানিকগত ধান মাড়াই পদ্ধতির পার্থক্য তেমন একটা হেরফের চোখে পড়েনি তবে এর যদি কোন আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান থেকেও থাকে তা আমার জানা নেই। তবে ছোট বেলায় অনেক বড় বড় মাড়া দেখেছি। দেখেছি ছাত্রাজীবনে রাজানগর হাইস্কুলে পড়ার সময় জমিদার বাড়িতে (পিলু চৌধুরী কাকু) থাকা অবস্থায়। আগেকার দিনে হাওরের বড় বড় গৃহস্থ যেমন- মহেন্দ্র মাস্টার (আঙ্গারুয়া, শাল্লা), জয়দেব বাবু (আবদা, শাল্লা), তারা মিয়া (কাশিপুর, শাল্লা), রাজেন্দ্র ডাক্তার (সুখলাইন, শাল্লা), শরৎ মেম্বার (বন শিবপুর, খালিয়াজুড়ি), গকুল বাবু (রওয়াইল, খালিয়াজুড়ি), গকুল সরকার (রওয়াইল কাদিরপুর, খালিয়াজুড়ি) উনাদের বাড়ির বড় বড় মাড়া হাওরে হাঁটলেই চোখে পড়ত। আর সমানে তুলনামূলক ছোট ছোট গৃহস্থদের মাড়া তো, হাওরজুড়েই থাকতো। এখনের দিনের জন্য এসব গল্প মনে হবে। আর ধান মাড়াই মেশিন এসে, এখন এসব তো প্রায় উঠেই দিয়েছে। বাংলার ইতিহাস ঘাটলে ধানের নজির দেখা যায়। ধান চাষ প্রাচীন ভূমির মধ্যে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র ও গাঙ্গেয় অববাহিকার নি¤œভূমি অন্যতম। প্রাচীন পূর্ব বাংলার মহাস্থানে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দে এবং উয়ারী-বটেশ্বরে ৪০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধান চাষের প্রমাণ আছে। প্রাচীন প্রতœতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাংলা ভাষার প্রথম রচনা চর্যাপদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে ধানের কথা দেখা যায়। তাই ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষের এই প্রধান খাদ্যশস্য, তার উত্তোলন বা সংগ্রহ স¤পর্কে লিপিবদ্ধ করণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যথায় নতুন প্রজন্মের কাছে ‘ধান মাড়া’ বা ‘ধান মাড়াই’ করা গল্পের মতো লাগলেও এক সময়ের পালের-নৌকার মতো শব্দদ্বয়ের বিলুপ্ত ঘটবে।
লেখক- সুশান্ত দাস, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী, সেন্টক্যালিক্সট, কানাডা।
নিউজটি আপডেট করেছেন : SunamKantha
ধান মাড়াই
- আপলোড সময় : ০৪-০৫-২০২৫ ০১:০৩:৩৫ পূর্বাহ্ন
- আপডেট সময় : ০৪-০৫-২০২৫ ০১:০৭:০৯ পূর্বাহ্ন

কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ
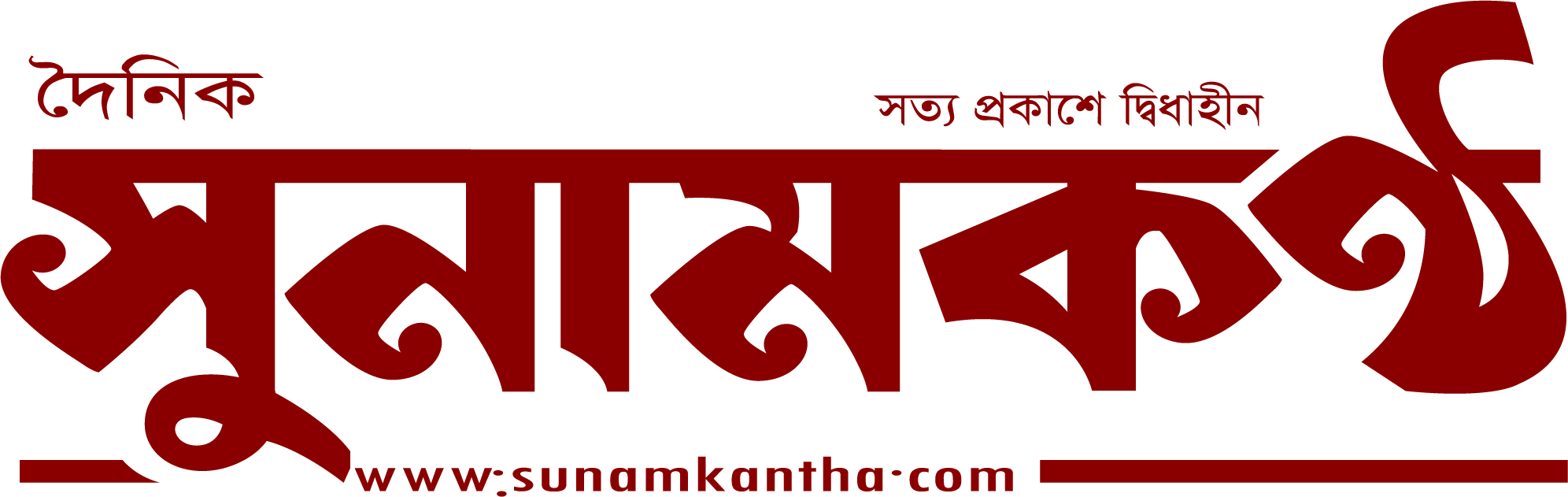
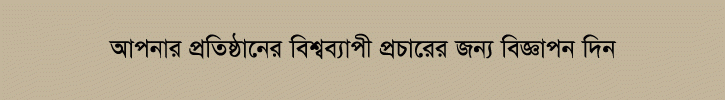

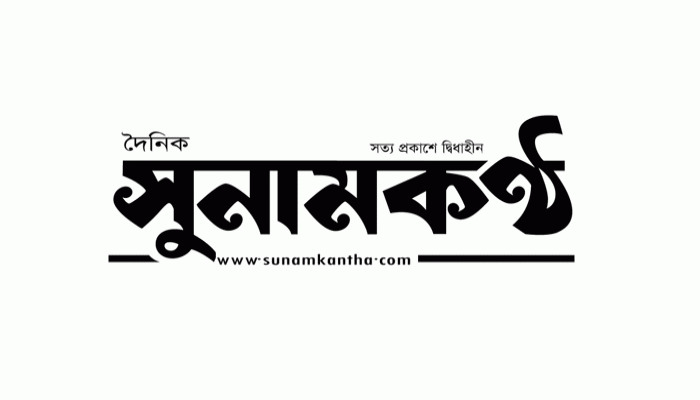 সুনামকন্ঠ ডেস্ক
সুনামকন্ঠ ডেস্ক