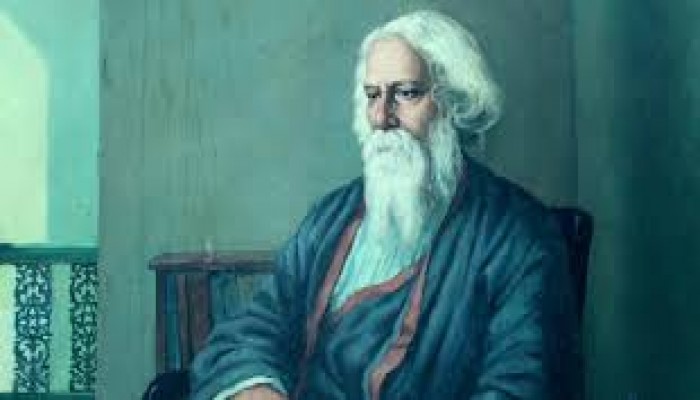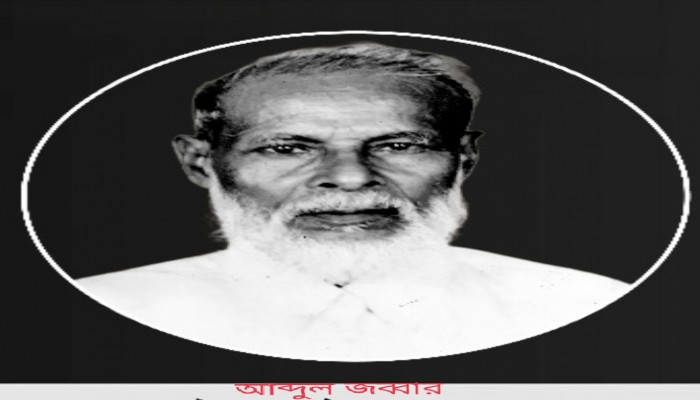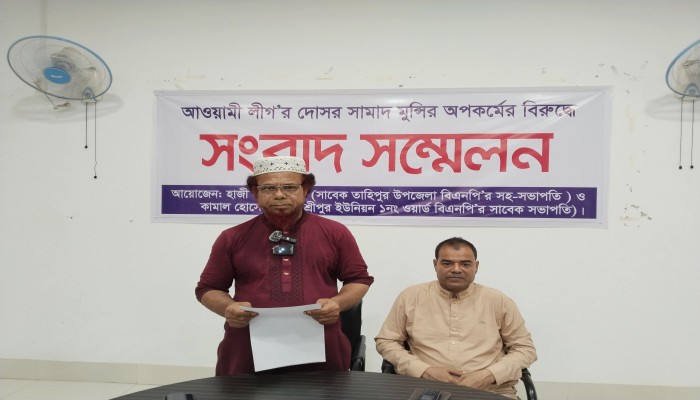ইকবাল কাগজী:
একদা দাসতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মুক্তির আকাঙ্খা থেকে স্পার্টাকাস নামের এক ক্রীতদাসের নেতৃত্বে ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি জাগরণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল, ইতিহাসে যা দাসবিদ্রোহ নামে বিখ্যাত। বলা হয়েছে, তখন “... দাসদের রোমানরা সমবেত দর্শকদের সামনে যুদ্ধ করিয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে বাধ্য করত এবং এক বিকৃত আনন্দ লাভ করত। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ৭৮ জন দাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে পালিয়ে যায় এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি করে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে। রোমান সৈন্যরা বারবার স্পার্টাকাসের কাছে পরাস্ত হয়। পরিশেষে, রোমান সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রাসসাসের হিংস্র আক্রমণে বিদ্রোহ দমিত হয়, ১২.৩০০ দাসসৈন্য বীরের মৃত্যুবরণ করে।” (হাওয়ার্ড ফাস্ট, স্পার্টাকাস, অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা : ৬)। ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দাসদের প্রতি তাদের প্রভুদের আচরণ নির্মম ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, যে-নির্মমতার কোনও তুলনা হয় না। কেবল নির্মম ছিল বলা বোধ করি সঙ্গত নয়, তার সঙ্গে ‘অমানবিক বীভৎস’ শব্দবন্ধের চয়ন জরুরি। তার নমুুনা হাজির করছি। উক্ত স্পার্টাকাস উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম ক্লডিয়া। সে ধনী মালিক আনতোনিয়াসের অতিথি। লম্পট আনতোনিয়াস তাকে খামারের আস্তাবলের কাছে বেড়াতে নিয়ে গেছে। “‘ক্লডিয়া লক্ষ্য করে আনতোনিয়াসের খামারের গোলামেরা কী চমৎকার শিক্ষিত এবং চতুর এবং প্রভুর প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি চাহনি ওরা আগে থাকতেই বুঝতে পারে। দাসদের মধ্যেই বড় হয়েছে ক্লডিয়াÑ সে জানে এদের নিয়ে কত হাঙ্গামা। একথা আনতোনিয়াসকে বলতে সে বলল : “আমি আমার গোলামগুলোকে চাবুক টাবুক মারি না। গোলমাল করলে ¯স্রেফ একটাকে খতম করে দি। তারপরে বাছাধনেরা আর টু শব্দ করেন না। বেশ মন দিয়ে কাজ করে।” “ভারি চটপটে ওরা, কাজে বেশ উৎসাহ আছে।” ক্লডিয়া বলে। “গোলামের জাতকে চালানো ভারি কঠিন এই গোলাম আর ঘোড়া। মানুষ চালানো অনেক সোজা।” (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪)। তৎকালের রোমান সমাজের অবস্থাটা এমন অমানবিক ও বর্বর, সেখানে আনতোনিয়াসের মতো দাস মালিকরা দাসকে একটি ঘোড়ার চেয়ে বেশি কীছু মনে করে না, সর্বোপরি দাসহত্যা একটা মামুলি ব্যাপার, অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়। অর্থাৎ দাসরা তাদের কাছে হাঁস-মুরগি, গরু-ভেড়া-ছাগলের মতো গৃহপালিত প্রাণী মাত্র। দাস একটি উৎকৃষ্ট পণ্য, দাসকে নিয়ে ব্যবসা চলে স্থানে স্থানে দাসবাজার বসে, এমনকি দাসকে হত্যা করে মাংস বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে তৃপ্তিবোধ করে, সাধারণ মানুষের অজান্তে অসৎ ব্যবসায়ীরা সে-মাংস দিয়ে মজাদার খাদ্য বানিয়ে বিক্রি করে। অবশ্য তার কারণও ছিল। কেননা রোমান রাজনীতিক সমাজ (যারা তখন রাষ্ট্র ও সমাজের অধিপতি, এককথায় মালিক ছিল) দাসদেরকে কাজের (আসলে উৎপাদনের) যন্ত্রের চেয়ে অধিক কীছু বলে মনে করতো না। হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর উপন্যাস স্পার্টকাস-এর এক চরিত্রের সংলাপ থেকে দাসদের প্রতি রোমান দাসমালিকদের মানসতা প্রতিপন্ন হয়েছে। দাসদের সম্পর্কে চরিত্রটি বলেছে, “ওরা হচ্ছে যন্ত্র সবাক যন্ত্র। আর জানোয়াররা আধা-বাক-যন্ত্র। সাধারণ যন্ত্র জানোয়ারদের থেকে আলাদা এগুলো বোবা যন্ত্র। ... গোলামরা শুধু সবাকযন্ত্র নয় তার চাইতে অনেক বেশী।” (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩০।) বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না যে, এখানে ‘সাধারণ যন্ত্র’ বলতে লাঙ্গল, কোদাল, শাবল, তীরধনু, তরবারি, চাবুক ইত্যাদি জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের হাতিয়ারকে বুঝানো হয়েছে। সত্যি কী ভয়ঙ্কর! এদিক থেকে পশুসমাজ উন্নত না হলেও, বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অপারগ হলেও, আন্তর্জালিক (ইন্টারনেট) সাংস্কৃতিক পণ্য গণনাযন্ত্র (কম্পিউটার) কিংবা মুঠোফোন ব্যবহার না করলেও তারা সত্যিকার অর্থে অনেক অনেক উত্তম। তারা প্রাকৃতিক নিয়মে একে অপরকে ভক্ষণে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু স্বস্বার্থে আঁতেল হয়ে উঠে পরিকল্পনা করে খুন করে না। তাদের সমাজে অর্থনীতি নেই বলে শোষণ নেই, শোষণ নেই বলে রাজনীতি নেই, রাজনীতি নেই বলে যুদ্ধ নেই, যুদ্ধ নেই বলে হত্যা-গণহত্যা, আধিপত্য ও ঔপনিবেশিকতা নেই। বলতেই হয় : মানুষের ইতিহাস হলো শোষণের ইতিহাস আর শোষণের ইতিহাস মানেই রাজনীতির ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস মানে সন্ত্রাস, খুন আর আধিপত্যের ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস। শোষণক্রিয়া না থাকলে এতোসব কীছু হতো না, হতো না দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ। এই সন্ত্রাস, খুন ও আধিপত্যের সমাজবাস্তবতা থেকে মুক্ত হওয়াই মানবতা অর্থাৎ মুক্তি। এইভাবে ভাবলে মানবতা এবং মুক্তি সমার্থক হয়ে উঠে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আগের চেয়ে, অর্থাৎ ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার পূর্বাপর পৃথিবীর থেকে বর্তমান পৃথিবীটা কি সত্যি সত্যি বদলে গেছে ? বদলেছে তো বটেই। বিজ্ঞানের অকল্পনীয় বিপুলবিশাল বিকাশবিস্তার ঘটেছে। তখন বর্শা-ধনুতীর-তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ হতো, এখন হয় মিসাইল, ড্রোন, জীবাণু, রাসায়নিক পদার্থসহ আন্তর্জালিক ভাইরাস দিয়ে। কিন্তু তারপরেও, এতোসব বদলের পরেও, আসলে কি বদলেছে ? মর্মগত দিক থেকে আসলে একেবারেই বদলে নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে বদলাতে বদলাতে বদলে যায় নি। তা হলে ব্যাপারটা কী ? ব্যাপারটা অনেকটা নির্মোক (সাপের খোলস) বদলের মতো। খোলস বদলে গেলে সাপটা বদলে যায় এমন তো নয়, সাপ তো সাপই থাকে, তার বিষদাঁত নির্বিষ হয়ে যায় না। আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কাঠামো বদলেছে বটে, সম্পদে ব্যক্তিমালিকানার ধরণ বদলে গেলেও তার অন্তর্নিহিত মর্মসার বদলে যায় নি, সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা থেকেই গেছে, শোষণের বিষদাঁত আরও প্রখরতা অর্জন করেছে। এই থাকটাই সমাজ আর সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। মানুষ সম্পদ সঞ্চয়ের মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই তো মাত্র ক’দিন আগে রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার গরিব উপেনের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। কবি লিখেছেন, “এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি / রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।” ইসরাইল ১৯৪৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জমি দখল অব্যাহত রেখেছে। উপেনের কিংবা ফিলিস্তিনের এই নিঃস্ব হওয়ার প্রক্রিয়া ও জমিদার বাবু কিংবা ইসরাইলের এই সম্পত্তিবৃদ্ধির পেছনের কারণ কী ? মর্মোদ্ধার করতে গেলে প্রত্যক্ষ কারণ মেলে সম্পদসঞ্চয় কিংবা সম্পত্তির পুঞ্জিভবন ব্যক্তি-গোষ্ঠী-চক্র অথবা শ্রেণি বিশেষের, আরও বৃহৎ পরিসরে রাষ্ট্রের তরফে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এর পেছনে কারণ অবশ্যই আছে। আর সে কারণ হলো সমাজে উদ্বৃত্তদ্রব্য আত্মসাতক্রিয়া থেকে গেছে, অর্থাৎ শোষণ বন্ধ হয়ে যায় নি, উদ্বৃত্তদ্রব্যের মোড়কে উৎপাদকের শ্রমশক্তি শোষণ অব্যাহত আছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক শ্রমবিভাগের উদ্ভবের ফলে উদ্বৃত্তদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয় এবং এর অনিবার্য পরিণতিতে সম্পত্তির মালিকানায় বৈষম্যের আবির্ভাব ঘটে। এই বৈষম্যের প্রেক্ষিতে ক্রমানুসারে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব, গোষ্ঠীব্যবস্থায় ভাঙন, বৈরীশ্রেণিসমূহের আবির্ভাব ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এই রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা পর্যন্ত দীর্ঘ কালপর্বের ব্যাপক পরিসরে উদ্বৃত্তদ্রব্য আত্মসাতের প্রক্রিয়া কমবেশি রূপান্তরিত রূপে থেকেই গেছে। অর্থনীতিবিদেরা কেউ কেউ এটিকে উদ্বৃত্তশ্রম কিংবা উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাত রূপে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিবেচনায় উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকের শ্রম শোষণের প্রক্রিয়াই বহাল থেকেছে এবং সেটা বহুগুণে বেড়েছে। একজন বলেছেন, “উদ্বৃত্ত শ্রম ছিল পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের আগেও। মানুষের উপর মানুষের যেকোন শোষণই, বাস্তবিকপক্ষে, শোষিত শ্রেণীর উদ্বৃত্ত শ্রমটাকে শোষক শ্রেণীর আত্মসাৎ করার ব্যাপার।” (ল. লেওন্তিয়েভ, অর্থশাস্ত্র : সংক্ষিপ্ত পাঠ্যধারা, অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রগতি প্রকাশন : মস্কো, ১৯৭৫, পুষ্ঠা : ৬৫।) অপরদিকে পুঁজিতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, পুঁজিতন্ত্র হলো এমন এক ব্যবস্থা “যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের মালিক, উৎপাদন চলে মজুরি শ্রম শোষণ করে।” (গেন্নাদি বেলভ, রাষ্ট্র কী, অনুবাদ : ননী ভৌমিক, প্রগতি প্রকাশন ; মস্কো, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা : ১৩৯।) উদ্বৃত্তশ্রম শোষণক্রিয়া থেকেই পুঁজির উদ্ভব ঘটেছে এবং কালক্রমে পুঁজি পৃথিবীর প্রভু হয়ে উঠে এমন এক অবস্থায় গিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, “যে অবস্থায় ... উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্যে লালসার কোন সীমাপরিসীমা থাকে না। মজুরি-দাসদের উপর শোষণ প্রচ-তর করার জন্যে পুঁজিপতিরা যেকোন এবং যাবতীয় উপায়ই ধরে। মার্কস বলে গেছেন, উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্যে পুঁজির লালসা নেকড়ের মতোই হিং¯্র।”(ল. লেওন্তিয়েভ, অর্থশাস্ত্র : সংক্ষিপ্ত পাঠ্যধারা, অনুবাদ : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, প্রগতি প্রকাশন : মস্কো, ১৯৭৫,পৃষ্ঠা : ৬৬।) এই হিংসতার প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীতে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে। তদুপরি পুঁজিতন্ত্র ইতোমধ্যে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ প্রসব করেছে। এই যুদ্ধের কারণ কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, “প্রায় সকল যুদ্ধের মূলে থাকে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্যগত স্বার্থ। তাহা হইতেই দেখা দেয় রাজনৈতিক সংকট এবং সেই সংকট হইতেই আরম্ভ হয় যুদ্ধ।” (সুপ্রকাশ রায়, পরিভাষা কোষ, র্যাডিক্যাল কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা : ২৬৭, স্তম্ভ : ১।) যুদ্ধ একটি বিশাল প্রপঞ্চ। এছাড়াও অনেক ছোট, বড় ও মাঝারি বিষয়প্রপঞ্চ জায়মান আছে বিশ্বের যে-কোনও দেশে যে-কোনও সমাজের অলিগলি কানাগলিতে। যেমন আমাদের দেশে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, রাহাজানি, পকেটমার, ব্যাংক লুট, বুঙ্গার কারবার, মাদকব্যবসা, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যবাণিজ্য, প্রতারণা, জালিয়াতি, মনোনয়ন বাণিজ্য, মানবপাচার, জিম্মি করে টাকা আদায়, জমি-বাড়ি-মাঠ-চর-নদী দখল, সরকারি সম্পত্তি-রাস্তা-ফুটপাত দখল, বালু-পাথর-পাহাড় লুট, ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, কারচুপি, গুম, অপহণ, খুন, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও বেকারত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব কীছুর মূলে আছে সেই এক প্রপঞ্চ, তার নাম শোষণ। শোষণ একমাত্র বিষবৃক্ষ যার মূল সমাজের গভীরে প্রোথিত ও শতসহস্র ডাল-পালা চতুর্দিকে বিস্তৃত। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তার উৎপাটন চাই। বাংলাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তার হরেক রকম বালাই আছে পদে পদে, পরতে পরতে। যেমন : নারী ভারতে পাচার হয়ে কোনও বেশ্যাপল্লীতে নিপীড়িত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, উপার্জনের আশায় বিদেশে গিয়ে স্বদেশী কোনও তঞ্চকের খপ্পরে পড়ে বিদেশের কোন বন্দিখানায় জিম্মি হয়ে স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের উপায় হয়ে উঠেছে কোনও যুবক, একজন থানা কর্মকর্তা সম্পদসঞ্চয়ের লালসায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ হাতানোর চক্র গড়ে তোলে একের পর এক খুন করতে পর্যন্ত পিছপা হচ্ছে না, আওয়ামী লীগ আমলে পাচার হয়েছে ২৮ লাখ কোটি টাকা, চার লাখ কোটি টাকা লুটে নেবে আদানি, অনেক শিক্ষক শিক্ষাবাণিজ্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং বাজারে সরকার মুদ্রিত পাঠ্যবই পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু অতিরিক্ত দামে বাজারে পাইরেসি ও পিডিএফ পাওয়া যাচ্ছে, চাষী ধান বা সবজির ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। এমন হলে তখন বুঝতে হবে যে, সমাজে শোষণপ্রপঞ্চ ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং আপাদমস্তক নষ্ট রাজনীতির খপ্পরে পড়ে সমাজ কাঠামোগত সহিংসতার করতলে তরপাচ্ছে, অপরাধের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে দেশ এবং মানুষ সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। এর নির্গলিতার্থ একটাই : এতোসব কা-কারখানার পেছনে আদি ও অকৃত্রিম কারণের নাম শোষণ। আপাতত দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বলে কোনও কীছুর অস্তিত্ব আসলেই কোথাও নেই, তথাকথিত সভ্যতার সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত কোনও দিন ছিল না। বিগত শতকের শেষার্ধ থেকে অদ্যাবধি, এর আগের কথা বলছি না, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সংঘটিত রাজনীতিক খুনগুলো তার প্রমাণ। মহাত্মা গান্ধি, লিয়াকত আলী খান, গোলাম কদ্দুস, সবদর হাসমি, সিরাজ সিকদার, শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা (তাজ উদ্দিন, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর), মেজর জিয়াউর রহমান, বন্দর নায়েক, ইন্দিরা গান্ধি, রাহুল গান্ধি, বেনজির ভুট্টো সবাইকেই হত্যা করা হয়েছে। সুনামগঞ্জও তার ব্যতিক্রম নয়, এখানকার কবি প্রজেশ কুমার রায়, কমরেড রবি দাম খুন হয়েছেন রাজনীতির হাতে। অর্থাৎ রাজনীতির পাকে পড়ে তাঁরা কেউই নিরাপদ ছিলেন না, আর এখনও কেউ নিরাপদ নন? আর নিরাপত্তা না থাকলে শান্তিও থাকে না। বর্তমান পৃথিবীতে অতীতের চেয়ে ভিন্ন প্রেক্ষিত-পরিস্থিতির পরিসরে কি আগের মতোই বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর নির্মম হত্যাকা- ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে না ? গত শতকের প্রথমার্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, ১৯৭১-য়ে বাংলাদেশে যুদ্ধ, প্রায় পৌনে একশত বছরব্যাপী ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ-বিরোধ ও সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ, রোহিঙ্গা সমস্যাসহ বিশ্বজুড়ে এমনতর আরও অনেক কীছু কী প্রতিপন্ন করছে ? প্রতিপন্ন করছে যে, প্রেক্ষিত-পরিস্থিতি যতোই বদলে যাকÑ আর্থসামাজিক বিন্যাসকাঠামো দাসতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে পর্যবসিত হোক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গহনে সেই আদ্যিকালের দাস-প্রভুর সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক চরিত্র বদলে যায় নি একটুকুও, যেমন ছিল তেমনটাই আছে নয় বরং আগের চেয়ে কৌশলী ও ভয়ঙ্কর নির্মম হয়ে উঠেছে। ৭১ খিস্টপূর্বাব্দে দুই দাসের মধ্যে লড়াই (যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে কোনও একজনের মৃত্যু পর্যন্ত দাসমালিকরা অপেক্ষা করতো) আর পরস্পরের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন-ইসরাইলের মানুষদের লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? শেষ বিচারে দুটিই খুনের নামান্তর, ভেতরে ভেতরে সেই আদ্যিকালের দাস-প্রভুর সামাজিক সম্পর্কের মতো, খুন করিয়ে আনন্দ লাভ। তাছাড়া পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রমিক সরাসরি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্ত মানুষ হতে পারে নি, শ্রমদাসে পর্যবসিত হয়ে ঐতিহাসিক পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতকের আগের শতকেই উন্নত প্রাযুক্তিক কৌশলের বদৌলতে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যাপক দক্ষতার সঙ্গে শ্রমিকের শ্রম শোষণ কারার জন্যে নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষে জনসমাজকে মারতে কসুর করছে না বিশ্ব পরিচালক পুঁজিতান্ত্রিক রাজনীতিক সমাজ। তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় গত শতকের সাহিত্যিক ভাবুক হাওয়ার্ড ফাস্ট যখন বলেন, “আজকের সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে প্রাচীন সুসভ্য রোমের ভীষণ মিল এই দুই প্রভুদের নৈতিক চরিত্র এতই অধঃপতিত যে এমন কোনো অন্যায় নেই যা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এরই মধ্যে আমরা স্পার্টাকাসের স্বপ্নময় বাস্তব পৃথিবীর পরিণতি সম্ভাবনার পাশাপাশি বাস করছি স্থানকাল নিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার জন্য মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস রচনায়।” (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬)। এতোক্ষণের বাকবিস্তারের মর্মার্থ করতে গিয়ে যে কেউ সেটাকে ‘স্পার্টাকাসের স্বপ্নময় বাস্তব পৃথিবীর’ সঙ্গে একাত্ম করে দিয়ে বলতেই পারেন যে, ক্রীতদাস স্পার্টাকাস ও তাঁর দাস সঙ্গীরা রোমান দাসমালিকদের দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, যেটাকে বলা যায় মুক্ত মানুষ হতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে মুক্তমানুষ সেই হতে পারে, যে-মুক্তমানুষ আর অন্য কোনও মানুষের প্রভু হয়ে উঠবে না, ব্যক্তিগত সম্পদসঞ্চয়ের লোভে মানুষের রক্তপাতে উন্মাদ হয়ে উঠবে না। স্পার্টাকাস ও তাঁর সঙ্গীরা যেখানে ছিলেন সেখানে মুষ্ঠিমেয় সম্পদসন্ধানী মানুষ অবশিষ্ট বিপুলসংখ্যক মানুষের শ্রমশক্তি শোষণের সামাজিক ব্যবস্থাকাঠামো কায়েম করে সে-ব্যবস্থাকাঠামো থেকে মানুষের মুক্তি ও মুক্ত মানুষের সমাজব্যবস্থা কায়েমের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছিল। স্পার্টাকাসের সময়ের সমাজের অর্থাৎ শ্রমশক্তি শোষণনির্ভর সমাজের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমাজ বাস্তবে দেখা দিয়েছে গত শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাবধি ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং তার পতন ঘটেছে পুরো সাত দশক পরে, যে-সমাজব্যবস্থাটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। রাশিয়াতে উদ্ভূত এই ব্যবস্থাটি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এতো বিখ্যাত কেন ? এর মধ্যে কী এমন আছে যে, সে-ব্যবস্থাটির পরিসরে মানুষের মুক্তি মিলে, যে-মুক্তিটি পুঁজিবাদের পরিসরে মিলে না ? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সমাজতন্ত্র কী, তা আগে জানতে ও বুঝতে হবে। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন বলেছেন, “সমাজতন্ত্রে থাকে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ বিলুপ্ত, জাতীয় অর্থনীতি বিকশিত হয় মেহনতিদের স্বার্থে একক পরিকল্পনা অনুসারে, ক্রমশ গড়ে ওঠে সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের সমান পরিস্থিতি।”(গেন্নাদি বেলভ, রাষ্ট্র কী, অনুবাদ : ননী ভৌমিক, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ; ১৪১।) অর্থাৎ সমাজে প্রত্যেকের জন্য সমানাধিকারের প্রতিষ্ঠাসহ শোষণমুক্ত শ্রমভিত্তিক এক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা জনগণের অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমাজের প্রতিটি সদস্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিশ্চিত করে। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগের ব্যবস্থাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সেগুলোতে উদ্বৃত্তশ্রম শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে কাঠামোগত সহিংসতার শিকারে পর্যবসিত হয়ে ছিল শ্রমজীবী মানুষেরা এবং এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকাঠামোর আধুনিকোত্তর রূপান্তর নয়া-ঔপনিবেশিকতার পতাকাতলে তেমনই শোষিত ও নির্যাতিত হয়েই আছে। এমন কাঠামোগত সহিংসতার পরিসর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুক্তি ও মুক্তমানুষের অস্তিত্ব একটি অবান্তর প্রাপঞ্চিকতা মাত্র। কিন্তু পৃথিবীতে স্পার্টাকাসের উত্তরসূরিরা সংগ্রাম এখনও অব্যাহত রেখেছে। কাঠামোগত সহিংসতাকে সমূলে উৎপাটনের সংগ্রাম চলছে এবং চলবেই এবং শোষণ নির্মূল হবেই। পৃথিবীর একমাত্র গন্তব্য তাই ‘স্পার্টাকাসের স্বপ্নময় পৃথিবীর পরিণতি’র দিকে।
নিউজটি আপডেট করেছেন : SunamKantha
মুক্তি ও স্পার্টাকাসের স্বপ্নময় পৃথিবী
- আপলোড সময় : ২৬-০১-২০২৫ ১১:৫২:৫৫ অপরাহ্ন
- আপডেট সময় : ২৬-০১-২০২৫ ১১:৫৪:৫৮ অপরাহ্ন
 ছবি: লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ইকবাল কাগজী
ছবি: লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ইকবাল কাগজী
কমেন্ট বক্স
সর্বশেষ সংবাদ
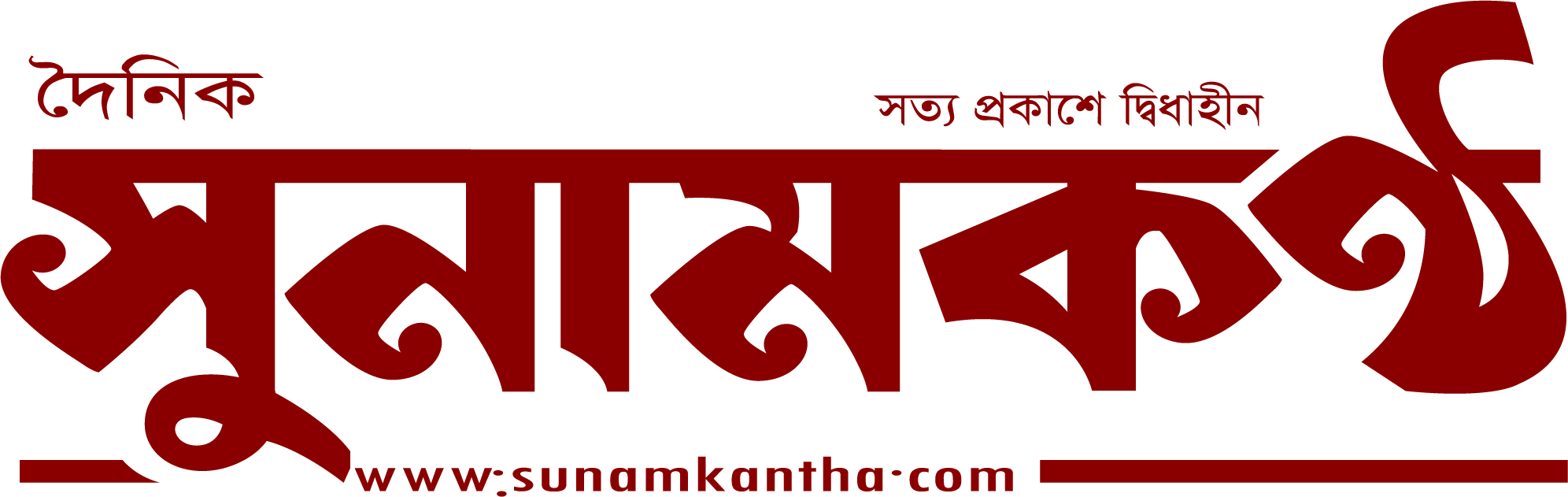
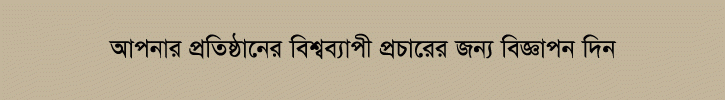

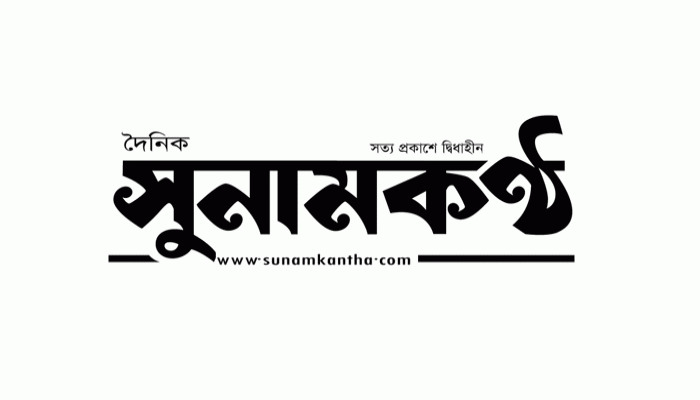 সুনামকন্ঠ ডেস্ক
সুনামকন্ঠ ডেস্ক