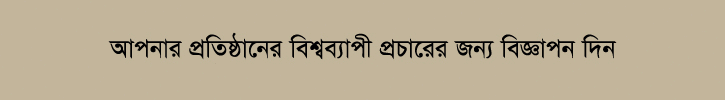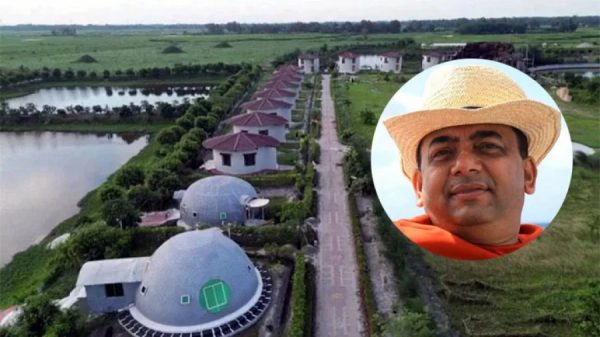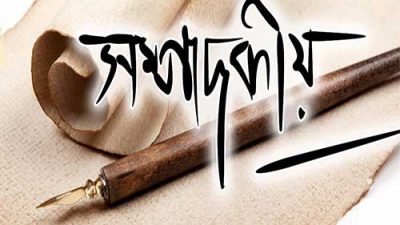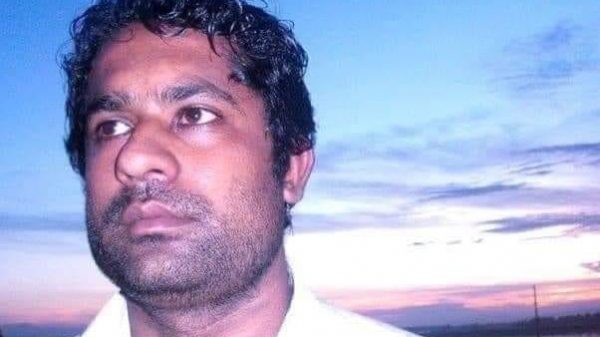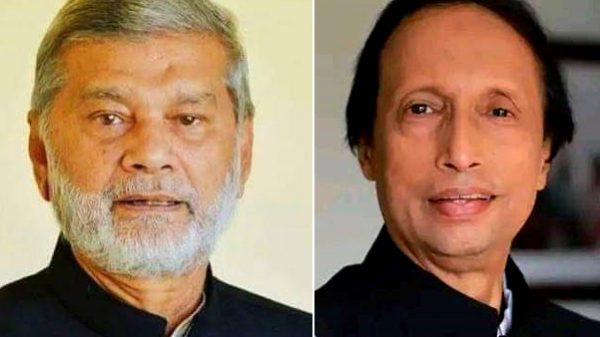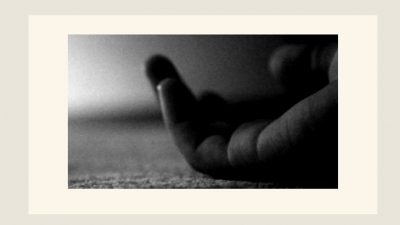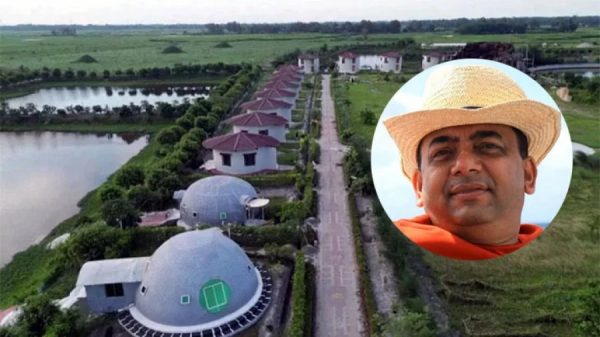পরিবর্তনের আশায় নাগরিক : মামুনুর রশীদ
- আপডেট সময় শুক্রবার, ২৪ মে, ২০২৪

বেশ কয়েক দিন ধরেই শহরের কিছু কিছু এলাকায় ফুটপাতগুলো পরিষ্কার হয়েছে। দোকানপাট নেই, ভ্যানগাড়িতে সবজির দোকানও নেই। স্বাচ্ছন্দ্যে পথচারীরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটার একটা অধিকার পেয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ফুচকা-চটপটির দোকান উঠে যাওয়ায় ওখানকার যে আড্ডা বা জটলা হতো, তা-ও এখন নেই। কয়েক যুগ ধরে যত্রতত্র বাজার বসে যাওয়ার যে প্রবণতা ছিল, তা এখন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কত দিন বন্ধ থাকবে? এসব দোকানপাটের অভিভাবক ছিল পুলিশ এবং এলাকার ক্ষমতাধর মাস্তান গোষ্ঠী। নিয়মিত চাঁদাবাজির মাধ্যমে অনেক দিন যাবৎ এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের দুপুরের খাবারের হোটেলও ছিল।
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের অসুবিধা হলেও কেউ এর বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ এখনো তোলেনি। অনেকের ধারণা, কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে যাবে। আবার ফুটপাত ও রাস্তাঘাটে ব্যবসা ফিরে আসবে। অতীতে অনেকবার হয়েছে, আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। অনিয়মই এখানে ঠিকঠাক। নিয়মটা একধরনের বিশৃঙ্খলা। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষেরা বিশৃঙ্খলাকেই বলে শৃঙ্খলা।
এদিকে ব্যাটারিচালিত রিকশাও নিষিদ্ধ হয়েছিল, চালকদের আন্দোলনের মুখে আবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বা যেকোনো জেলা শহরে যানজটের একটা বড় কারণ এই ব্যাটারিচালিত যানটি। কিছু কিছু মহাসড়কে, বিশেষ করে পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটাও ভালো উদ্যোগ। সারা দেশ মোটরসাইকেলে সয়লাব। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হিসেবেও এ যানটি দেখা দিয়েছে। নাগরিকদের কল্যাণে এবং সুবিধার জন্য এসব পদক্ষেপ যে কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ দিতে হয়।
কিন্তু এর মধ্যে একটা বড় ‘কিন্তু’ হয়ে দেখা দিয়েছে অন্য একটি বড় প্রশ্ন। প্রশ্নটি একেবারে জীবন-মরণের। সংক্ষেপে বাংলায় যাকে বলা হয় ‘জীবিকা’। এই যে শহরে লাখ লাখ ফুটপাত দোকানদার – তাঁদের জীবিকার ব্যবস্থাটা কী? তারা হয়তো একদা গ্রামেই বাস করত। কৃষি তাদের জীবিকা ছিল। কিন্তু সে জায়গাটা যখন জীবিকার জন্য অপ্রতুল শুধু নয়, শূন্য হয়ে গেল, তখন একা বা পরিবার নিয়ে এক অনিশ্চিত যাত্রায় রাজধানী বা বড় কোনো শহরে এসে তারা কায়ক্লেশে একটা জীবিকার ব্যবস্থা করে নিল। যেমন মাঝে মাঝে আমি একটা ফুটপাতের দোকানে চা খাই। দোকানদারের বাড়ি নদীর পাড় ভাঙা এলাকায়। তিন ছেলে, স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে নিয়ে কোনো এক বস্তি বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, মিষ্টি, পান নিয়ে তার দোকান। ছেলেরাও পর্যায়ক্রমে তার সঙ্গে কাজ করে। ঈদের সময় খদ্দেরদের কাছ থেকে বকশিশ মেলে। এভাবেই সপ্তাহের সাত দিন, সকাল থেকে নিশুতি রাত পর্যন্ত যতক্ষণ মানুষ পথে থাকে, ততক্ষণ তার দোকান খোলা থাকে।
রিকশার সংখ্যা ঢাকায় এখন কত এবং রিকশাওয়ালার সংখ্যা কত, তা হয়তো এখন আর কেউ বলতে পারবে না। আগে রিকশার পেছনে সিটি করপোরেশনের একটা লাইসেন্সের সাইনবোর্ড থাকত। এখন আর তা নেই, যেন সব আইনশৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে। বাসভাড়া নিয়ে দেনদরবার হয়, কিন্তু রিকশাভাড়া নিয়ে কোনো রকম দেনদরবার চলে না। ভাড়া ইচ্ছামতো বাড়ায় রিকশাচালকেরা। সে তার ইচ্ছামতোই চলে। ট্রাফিক আইনের ধার ধারে না। উল্টোপথে প্রায়ই তার যানটি চলে। ট্রাফিক পুলিশের লাঠিটি তার একমাত্র আইন। আর চার চাকার একটা যান চলে, তার নাম লেগুনা। চালক সাধারণত অল্প বয়সী। এই সব চালকের কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স বোধ হয় লাগে না। অসহায় নগরবাসীর জন্য কোনো কোনো এলাকায় এই বাহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো এলাকায় সে দাপিয়ে বেড়ায়। তার জন্য রাস্তার ওপরেই স্ট্যান্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় রাস্তার অর্ধেকজুড়েই তার স্ট্যান্ড। অবকাঠামো নির্মাণের বিপ্লবে চার লেন, ছয় লেনের রাস্তাতেও একটা বড় অংশই চলে গেছে স্ট্যান্ডওয়ালাদের দখলে। কোথাও কোথাও অকেজো ট্রাক-বাসের স্থায়ী আবাসস্থল সেগুলোই।
এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেমন মুশকিল, তেমনি এই পরিস্থিতি অনেকেরই অর্থ উপার্জনের একটা উপায় বের করে দিয়েছে। এই অর্থও কম অর্থ নয়। একটা শ্রেণির আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার ব্যবস্থাও করেছে। মাঝে মাঝে এর মধ্যেও কিছু সংস্কার উদ্যোগ দেখা যায়; কিন্তু তা যেমন সাময়িক, তেমনি অবাস্তবও বটে। আমাদের অর্থনীতির আকারটাও দিন দিন বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। বিদেশে যেমন হাজার হাজার কোটি টাকা এই নিরীহ বাঙালি সন্তানেরা লগ্নি করছে (মোটামুটি অন্যায়ভাবে), তেমনি দেশেও বিভিন্ন ব্যবসায় লগ্নি বাড়ছে। অর্থনীতির ভাষায় ফরমাল ও ইনফরমাল খাত বলে দুটি মোটাদাগের খাত চিহ্নিত করা হয়েছে। যে দোকানটিতে আমরা চা খাই, যে হকারের কাছ থেকে মাছ-তরকারি-ফলমূল কিনি, তার ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার কোনো বালাই নেই, ভ্যাট-ট্যাক্স তো নেই-ই। এই ইনফরমাল খাতের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সরকার কোনো ট্যাক্স পায় না। কিন্তু ট্যাক্স তাদের দিতেই হয়, চাঁদাবাজদের কাছে।
রিকশাওয়ালা বা মালিকদেরও একই অবস্থা। লেগুনার মালিকেরাও একই জায়গায় ট্যাক্স দিয়ে থাকে। তার মানে, দেশে সরকারি ট্যাক্স ব্যবস্থার সমান্তরালে একটা বড় ট্যাক্স ব্যবস্থা আছে। আবার যেখানেই প্রকৃতি স¤পদ ও জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকে, সেখানেও হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থনীতিটি এই ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। মৎস্য, বন স¤পদ, বালু উত্তোলন – এসবের মধ্যে যে ব্যবস্থাটি আছে, তা-ও এই অদৃশ্য সরকারের হাতে গিয়ে পড়েছে। দেশের ব্যাংকের এমডিরা বিদেশে যাচ্ছেন হুন্ডি বন্ধ করতে। দেশের মধ্যে সরকারের কোনো ক্ষমতাই নেই অবৈধ পাচার বন্ধ করার, এটা সত্যি।
কিন্তু ব্যাংকের এই শীর্ষ কর্মকর্তারা বিদেশে গিয়ে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে দেশে আসবে এবং কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না। এসবই আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল। পরিস্থিতি বিবেচনায় যা মনে হয় তাতে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, দেশের অর্থনীতি নিয়ে সুদূরপ্রসারী কোনো ভাবনা করা হয় না।
যে লোকগুলোকে নিয়ে কথা হলো, তাদের জন্য একটা স্থায়ী জীবিকার ব্যবস্থা আমরা ৫৩ বছরেও করিনি। রিকশা চালানোর মতো অমানবিক একটা শ্রম থেকে দরিদ্র মানুষের মুক্তির কথা আমরা ভাবলেও তার জন্য কোনো একটা কার্যকর পদক্ষেপও নিইনি। এত হাজার হাজার কোটি টাকা এল, এনজিও সেক্টরে তাদের যদি বাধ্য করা হতো যে রিকশাচালকদের জন্য একটা সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম নিতে হবে – তাহলেও একটা ব্যবস্থা হতে পারত। ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দরিদ্র মানুষদের ঋণের খাঁচায় বন্দী করার বিনিময়ে জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারত। একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সরকারের মধ্যে অর্থনীতিবিদ এবং পরিকল্পনাবিদ নেই। সবটা জায়গা দখল করে আছে আমলারা। এদের দেশ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, স্বপ্নও নেই। এরা সরকারকে সব সময় ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। আর ওই অতি ব্যস্ত রাজনীতিবিদ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামাল দেওয়ার কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে তার এদিকে তাকানোর কোনো উপায় থাকে না।
সচেতন জনগণও তাদের বিচার-বুদ্ধির বিবেচনাটি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। প্রতিদিনের সংকটে সে নিমজ্জিত। দু-একটি সংস্কারমূলক কাজেই সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আবার নিজের ভূমিকাটি না নিয়ে সরকারকেই দায়ী করে একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যদিও সমাজটা ভেঙে গেছে, তাকেও আবার জাগ্রত করার একটা দায়িত্ব নাগরিকদের আছে। সে কথাটি অবলীলায় ভুলে গেলেও চলবে না। সমাজের প্রতিটি নাগরিকের যে ভূমিকা, তা সঠিকভাবে পালন করতে পারলে একটা পরিবর্তন আসতেও পারে।